রামিসা রহমান : দেশি ব্র্যান্ডগুলোর পোশাক দেশেই তৈরি হচ্ছে। অথচ ঢাকার বাজারে এসব ব্র্যান্ডের পণ্যের দাম ইউরোপ ও আমেরিকার চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের স্থানীয় জনপ্রিয় ব্র্যান্ড আড়ং, আর্টিসান, ইনফিনিটি, ডিসেন্ট, রেড রিদম ও ইয়েলো ব্র্যান্ডের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্যের বাজার বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, এলিট শ্রেণির ক্রেতা ধরতে এ কৌশল নিচ্ছে ব্র্যান্ডগুলো। প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মূল্য নির্ধারণ করছে তারা। এর মধ্যে দিয়ে রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠছে প্রতিষ্ঠানগুলো।
বাংলাদেশ বিশ্বের গার্মেন্টশিল্পের অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক দেশ, যেখানকার তৈরি পোশাক ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগ নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে। এ দেশের শ্রমনির্ভর শিল্প বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর চাহিদা মেটাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে পোশাক বাংলাদেশে তৈরি হয়, তা কি বাংলাদেশিরা নিজের দেশে সাশ্রয়ী দামে কিনতে পারছেন? নাকি তারা সেই পণ্যের জন্য ইউরোপের ক্রেতাদের চেয়েও বেশি অর্থ ব্যয় করছেন?
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাদের পোশাকের দাম ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক সময়ই বেশি পড়ে যায়। ইনফিনিটির একটি সাধারণ কুর্তির দাম প্রায় ৪ হাজার ২০০ টাকা। অথচ এই মানের বা তারচেয়েও উন্নত মানের ওয়ান পিস ইউরোপের জারা, এইচ অ্যান্ড এম বা প্রাইমার্কের মতো স্টোরে মিলছে মাত্র ২০ থেকে ২৫ ইউরোতে। বর্তমানে ইউরোর বিনিময় হার এক ইউরো সমান ১৪২ টাকা ধরে হিসেব করলে এই দাম দাঁড়ায় ২ হাজার ৮৪০ থেকে ৩ হাজার ৫৫০ টাকার মধ্যে। সহজভাবেই বোঝা যায়, একই ধরনের পণ্যের জন্য দেশের ভোক্তাকে দিতে হচ্ছে বেশি মূল্য। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা দেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মতামত বিশ্লেষণ করি। এদিকে ইয়োলোতে একটা ওয়ান পিসের দাম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। একটা সালোয়ারের দাম ১ হাজার ২০০ টাকার ওপরে।
রফিকুল ইসলাম নামের একজন সরকারি চাকরিজীবী বলেন, আমরা এমন একটা দেশে থাকি, যেখানকার পোশাক বিশ্বজুড়ে রপ্তানি হয়। অথচ নিজের দেশেই যদি এই পণ্যের জন্য আমাদের বেশি দাম দিতে হয়, সেটা কতটা যুক্তিসংগত?
আবার একই ধরনের মত প্রকাশ করেন বেসরকারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কর্মী আতুল চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘আমি সম্প্রতি ইনফিনিটি থেকে একটি শার্ট কিনেছি চার হাজার ৫০০ টাকায়। অথচ আমার বোন স্পেনে জারা থেকে কিনেছে ২৫ ইউরো দিয়ে প্রায় একই ধরনের পোশাক। মানেও খুব একটা পার্থক্য নেই।’
অন্যদিকে ইতালির মিলানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ফারহানা হক বলেন, আমি জারা বা ম্যাঙ্গোর মতো ব্র্যান্ড থেকে ডিসকাউন্টে ২০ ইউরোতে দারুণ কিছু কিনতে পারি। অর্থাৎ ২ হাজার ৮৪০ টাকায় আমি এমন পোশাক পাচ্ছি, যা বাংলাদেশে হয়তো ৪ হাজার ৫০০ টাকা ছাড়াও পাওয়া যাবে না।
লন্ডন প্রবাসী শারমিন নাহার শেয়ার বিজকে বলেন, প্রাইমার্কে ৩০ ইউরো দিয়ে জ্যাকেট কিনেছি, যেখানে ট্যাগে লেখা ছিল ‘মেড ইন বাংলাদেশ’। অথচ সেই একই জ্যাকেট দেশে গেলে ৪ হাজার ৫০০ টাকার নিচে পাবেন না।
মূলত কয়েকটি কাঠামোগত ও বাজারিক কারণে বাংলাদেশের বাজারে পোশাকের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রথমত, দেশে প্রতিযোগিতার অভাব এবং কিছু নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের একচেটিয়া বাজার দখলের প্রবণতা দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এসব ব্র্যান্ড নিজেদের লোকাল প্রিমিয়াম হিসেবে তুলে ধরলেও তাদের পণ্যের মূল্য তুলনায় অতিরিক্ত। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ভ্যাট, দোকানভাড়া, কর্মী খরচ এবং বিপণনের অতিরিক্ত ব্যয় সামগ্রিকভাবে পোশাকের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফলে সেটার প্রভাব পড়ে ভোক্তার ওপর।
বাংলাদেশে যেসব উপকরণ আমদানি করে পোশাক তৈরি হয়, সেগুলোর ওপর উচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ থাকে। একইসঙ্গে উৎপাদকরা স্থানীয় বাজারকে অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারের মতো ছাড় বা অফার দেয় না। ইউরোপে যেখানে জারা বা এইচ অ্যান্ড এম প্রায় সারা বছর ডিসকাউন্ট ক্যাম্পেইন চালায়, বাংলাদেশে সেসব অফার সীমিত এবং অনেক সময় কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে অফার দেয়া হয়।
অনেকে মনে করেন, একটি বিষয় যে ইউরোপে বিক্রি হওয়ার মতো পণ্যের মান বেশি ভালো, তাই দেশীয় বাজারে তারা ‘বিকল্প’ মানের বা ‘লোকাল ভার্সন’ কিনছেন বেশি দামে। বাস্তবে অবশ্য সেই পণ্যের উৎপাদন একই ফ্যাক্টরিতে হয়, শুধু ট্যাগ ও ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য দাম ভিন্ন হয়।
এসব বাস্তবতা মিলিয়ে যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়, তা হলো বাংলাদেশি ভোক্তারা তাদের নিজস্ব দেশে উৎপাদিত পোশাক কিনতেও ইউরোপীয় ভোক্তার চেয়ে বেশি টাকা গুনছেন। একদিকে রপ্তানি-পণ্য হিসেবে দেশের পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে দেশের ভোক্তার কাছে সেটিই যেন একপ্রকার বিলাসপণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আবার অনেকে মনে করেন, ভোক্তারাও এই দামের বৈষম্য নিয়ে সচেতন না বলেই ব্র্যান্ডগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করছে। দেশে এখনও ব্র্যান্ড সচেতনতা অনেকাংশে শহরকেন্দি ক এবং মিডল ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেখানে মূল্য যাচাই না করেই ‘ব্র্যান্ড ভ্যালু’ ধরে কেনাকাটা করা হয়। এই সুযোগটাই নিচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠান।
আর্টিসান এর সঙ্গে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করলে তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ইনফিনিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. নাজমুল হক খানের সঙ্গে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ইয়েলো ব্র্যান্ডের এক কর্মকর্তা শেয়ার বিজকে বলেন, ‘আমাদের প্রতিটি কাপড় দেশেই তৈরি হয় এবং কোয়ালিটির ব্যাপারে আমরা সবসময় আপসহীন। ক্রেতারা চাইলে সরাসরি এসে কাপড় দেখে যাচাই করতে পারবেন। আমরা বিশ্বাস করি, সর্বোচ্চ মানের কাপড়ই আমাদের ব্র্যান্ডের আসল পরিচয়।’
বাংলাদেশ ভোক্তা সমিতির (ক্যাব) সহসভাপতি এসএম নাজের হোসাইন বলেন, যারা এক্সপোর্ট করছে, সেখানে একরকম দাম বাইরে আনেকটা ব্যতিক্রম। এটা হওয়ার কারণ আমরা মনে করি কীভাবে তারা অধিক মুনাফা করবে। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে খবর আসে, অনলাইনে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করে দেড় কোটি টাকার মালিক। এর কারণে অনলাইন বা শোরুমে জিনিস একই কিন্তু দাম অনেক বেশি। আবার আড়ংও এর মধ্যে আছে। আড়ংয়ের কাপড় বাইরেও কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু আড়ংয়ের থেকে অর্ধেক দামে। শোরুমের ভাড়া, তাদের বেতন আর অন্যান্য খরচ ধরেও তারা দ্বিগুণ দাম ধরে কাপড় বিক্রি করতে পারে না। লাভের একটা পরিমাণ আছে। এসব জায়গাতে আমরা দেখছি মুনাফাটা অনেক বেশি। আসলে সমস্যাটা হলো মানুষ ভোক্তা অধিদপ্তরে বিষয়গুলো নিয়ে বললে তারা সময় জরিমানা করলেও পরে শোরুমগুলো খুলে দিতে বাধ্য হয় আইন দুর্বলতার কারণে। তারা বেশি টাকা নিচ্ছে, এই বিষয়টি কোনোভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না। আমরা এখন প্রথমের দামে ঠকছি, পরে মানেও ঠকছি। এককথায় আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। আইনে লিগ্যাল প্রোটেকশনগুলো ছিল, এগুলো না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেক নিম্নমানের কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে এসব ব্র্যান্ডগুলোয়। এর একমাত্র কারণ অতি মুনাফা করা। তা না হলে একটা কোম্পানির তার শোরুম বা গুড উইল নষ্ট করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। এসব ব্র্যান্ড প্রথমে একটা-দুটা কাপড় ভালো দিয়ে তারপরে গুলিস্তানের কাপড়ের মতো কাপড় ব্যবহার করে অতি মাত্রায় লাভ করছে। অনেক দোকানের বিক্রেতারা বলেন, এসব ব্র্যান্ড আমাদের থেকে কাপড় নিয়ে গিয়ে তারা তাদের শোরুমে বিক্রি করে।
তিনি বলেন, একটা ব্র্যান্ড আরেকটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকে যে, কে কত টাকা মুনাফা করতে পারে। তারা ব্যবসার নীতি-নৈতিকতা তো মেনে চলেই না, কীভাবে ফাঁকি দেবে, কীভাবে তারা মানুষ ঠকাবেÑএসব চিন্তাভাবনা করে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, লাভ বেশি করে ঈদের সময়। তারা নির্ধারিত মূল্যের ট্যাগ সরিয়ে নতুন মূল্যের ট্যাগ বসিয়ে অধিকতর লাভ করে। এ সময় ক্রেতারা চেক করার সময় পান না। তখন যে দামে থাকে সেই দামেই আমাদের ক্রয় করতে হয়। তখন আসলে কিছুই করার থাকে না। এ সুযোগে তারা ১০০ টাকার জিনিস ৫০০ টাকা করে দেয়।
আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সেলের নাম করে তারা নিম্নমানের মেয়াদোত্তীর্ণ কাপড়গুলোতেও তারা কেনা দামের অধিক মূল্য বসিয়ে লাভ করে।
সবশেষে দেখা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিদেশে বিক্রি হচ্ছে সাশ্রয়ী দামে, অথচ দেশেই সেই পণ্যের দাম অনেক বেশি এটি কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র নয়, বরং একটি নীতিগত অসামঞ্জস্য। যেখানে একটি দেশ বিশ্বের জন্য পোশাক বানায়, অথচ নিজেদের মানুষ সেই পোশাক সহজে কিনতে পারে না, সেখানে প্রশ্ন উঠেই যায়Ñএই শিল্প কার জন্য?
বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টর যদি সত্যিকার অর্থেই দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে, তবে তার সুফল দেশীয় ভোক্তারা পাচ্ছেন না কেন? আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সফল হলেও দেশীয় বাজারে যদি সেই পণ্য অতিরিক্ত দামে বিক্রি হয়, তাহলে সেটা ন্যায্যতা নয়, বরং বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করতে প্রয়োজন সচেতনতা, নীতি সংস্কার এবং ব্র্যান্ডগুলোর সামাজিক দায়িত্ববোধের বাস্তবায়ন।
 প্রিন্ট করুন
প্রিন্ট করুন

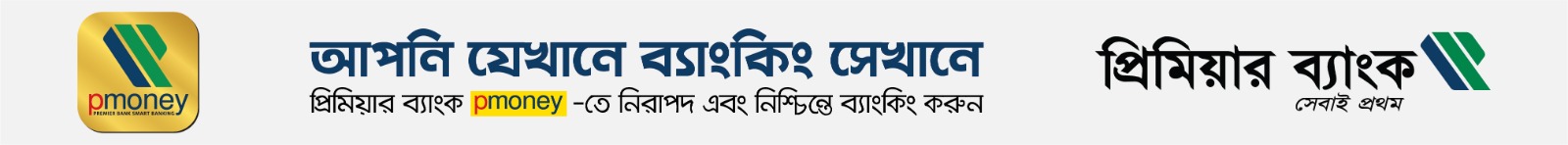










Discussion about this post