মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন : বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। জীবিকার প্রধান উৎস জমি, কৃষিকাজ ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কার্যক্রম। স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কৃষককে উৎপাদনশীলতার মূলধারায় আনা—এসব কিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। বিশেষ করে সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও কৃষি ব্যাংক কৃষি উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। ঋণ, ভর্তুকি, প্রকল্প অর্থায়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষকের হাতে নগদ প্রবাহ সৃষ্টি—এসব দিক থেকে তারা আসল চালিকাশক্তি।
বাংলাদেশের কৃষির যাত্রা সহজ ছিল না। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে খাদ্যাভাব ছিল তীব্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়—সব মিলিয়ে কৃষক উৎপাদনে টিকতে পারত না। এমন সময়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কৃষি খাতকে ব্যাংকঋণের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার। কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকের কাছে সহজ শর্তে ঋণ পৌঁছে দেয়া। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ধান, গম, ভুট্টা কিংবা ডাল চাষে কৃষকদের যেসব অর্থের প্রয়োজন হতো, তা সরাসরি সরবরাহ করত এই ব্যাংক। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক শাখা বিস্তৃত করে গ্রামে গ্রামে কৃষিঋণ পৌঁছে দেয়।
একজন কৃষকের বাস্তব উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। রাজশাহীর এক প্রান্তিক কৃষক শফিকুল ইসলাম একসময় মাত্র দুই বিঘা জমিতে ধান ফলাতেন। নগদ অর্থের অভাবে ভালো জাতের বীজ, সার, কীটনাশক কিনতে পারতেন না। স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিলে সুদের বোঝায় আরও ডুবে যেতেন। কৃষি ব্যাংক থেকে যখন প্রথম সহজ শর্তে ঋণ পেলেন, তখনই তার জীবনে পরিবর্তন আসে। সে টাকা দিয়ে উচ্চফলনশীল ধান চাষ শুরু করেন। উৎপাদন বেড়ে যায় দ্বিগুণেরও বেশি। পরে জনতা ব্যাংকের সহায়তায় একটি ডিপ টিউবওয়েল বসান, যার পানি দিয়ে শুধু নিজের জমিই নয়, পাশের কয়েক গ্রামের জমিও সেচ হয়। এভাবে একজন ক্ষুদ্র কৃষক ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে হাঁটেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুন গতি দেয়।
সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। আশির দশকে যখন দেশ খাদ্য ঘাটতিতে ভুগছিল, তখন কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা বাড়ানোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার সেই সময়ে নলকূপ, ডিপ টিউবওয়েল, সেচ পাম্প কেনার জন্য ভর্তুকি ঘোষণা করে। কিন্তু ভর্তুকির বাইরে প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান কোথা থেকে আসবে—সে দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। সোনালী ব্যাংক কৃষকদের সেচ পাম্প কেনার জন্য প্রকল্প ঋণ দেয়। হাজার হাজার কৃষক এভাবে সেচের আওতায় জমি আনতে সক্ষম হয়। ফলে ধান ও গম উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, যা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে দেশকে এগিয়ে দেয়।
কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণেও ব্যাংকগুলোর অবদান গভীর। শুধু ধান বা গম নয়, ফলন বাড়ানোর জন্য শাকসবজি, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের ঋণ দেয়া হয়। উত্তরবঙ্গের রংপুরে আজ আলুর যে বিপুল উৎপাদন দেখা যায়, তার পেছনে কৃষি ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের যৌথ ঋণ প্রকল্প বড় ভূমিকা রেখেছিল। ক্ষুদ্র কৃষকরা সংগঠিত হয়ে সমবায় আকারে ব্যাংক ঋণ নিয়ে আলু চাষ শুরু করে। উৎপাদন বেড়ে গেলে স্থানীয়ভাবে কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণেও ব্যাংক ঋণ দেয়া হয়। এর ফলে আলু শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও রপ্তানি শুরু হয়। একসময় যে কৃষকরা খাওয়ার মতো আলু পেতেন না, তারা আজ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন।
গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে যখন দেখা যায়, ব্যাংক ঋণের কারণে কৃষকের হাতে নগদ প্রবাহ তৈরি হয়। গ্রামের বাজারগুলোয় একসময় ক্রেতা ছিল কম, কেনাকাটা সীমিত ছিল। কিন্তু কৃষক যখন ঋণ নিয়ে আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে শুরু করে, তখন তাদের আয়ও বাড়ে। এ আয় থেকে তারা সন্তানের পড়াশোনায় খরচ করে, ঘর বানায়, ব্যবসা করে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারেই পাল্টে যায়। বাজারে দোকানপাট বাড়ে, হাটবাজার জমজমাট হয়, পরিবহন খাতে চাহিদা বাড়ে। এভাবেই ব্যাংক ঋণ শুধু কৃষি নয়, গ্রামীণ সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার গল্পে নব্বইয়ের দশকের সফলতাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের ধানক্ষেত তলিয়ে গেলে খাদ্য ঘাটতির শঙ্কা দেখা দেয়। তখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কৃষকদের জরুরি ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন দেয়। কৃষকরা আবারও মাঠে দাঁড়িয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ধান উৎপাদনে ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালের পর বাংলাদেশ ধীরে ধীরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ অর্জনের পেছনে কৃষকদের পরিশ্রমের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহজলভ্য ঋণ সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি।
মৎস্য ও পশুপালন খাতেও ব্যাংকের অবদান অবিস্মরণীয়। কুমিল্লার লাকসামে কামাল হোসেন নামের এক যুবক কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাছচাষ শুরু করেন। শুরুতে একটি ছোট পুকুরে রুই-কাতলা চাষ করতেন। পরে সোনালী ব্যাংকের সহায়তায় আরও বড় জলাশয় ভাড়া নিয়ে মাছচাষ বাড়ান। আজ তিনি একজন সফল মৎস্য উদ্যোক্তা, আশপাশের অন্তত ৫০ জন মানুষ তার খামারে কাজ করছে। একইভাবে কুষ্টিয়ার রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গরুর খামার গড়ে তোলেন। ঈদে কোরবানির সময় তিনি শত শত গরু বিক্রি করেন। এ উদাহরণগুলো শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো গ্রামীণ অর্থনীতিকে বদলে দেয়ার দৃষ্টান্ত।
কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ধান কাটার মেশিন, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর—এসব কিনতে কৃষকরা যখন দ্বিধায় ছিল, তখন কৃষি ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের যৌথ প্রকল্পে সহজ কিস্তিতে ঋণ দেয়া হয়। ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের কাজ সহজ হয়, উৎপাদন খরচ কমে, সময় বাঁচে। প্রযুক্তি ব্যবহারের এই ধারা আজ গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও টেকসই করছে।
এতকিছুর মধ্যেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল—খেলাপি ঋণ, রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা দুর্বল তদারকি। তবুও সামগ্রিক চিত্রে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে ওঠার পেছনে তাদের অবদান নির্ণায়ক। যদি এই ব্যাংকগুলো গ্রামীণ কৃষকের কাছে সহজ শর্তে ঋণ পৌঁছে না দিত, তাহলে হয়তো বাংলাদেশ আজও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত না।
আজ যখন বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে, তখন বাংলাদেশ গর্বের সঙ্গে বলতে পারে—আমরা নিজেদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এ অর্জন কোনো একক প্রচেষ্টার ফল নয়, এটি কৃষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও কৃষি ব্যাংক—তাদের প্রতিটি ঋণ প্রকল্পে লুকিয়ে আছে হাজারো কৃষকের ঘাম, হাজারো পরিবারের স্বপ্ন এবং একটি জাতির খাদ্য নিরাপত্তার ভিত।
 প্রিন্ট করুন
প্রিন্ট করুন

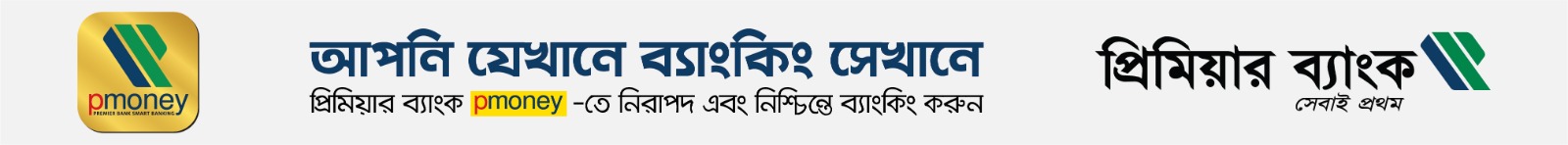











Discussion about this post