মোহাম্মদ হাফিজ আল আহাদ : বাংলাদেশের আর্থিক খাত— ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (ঘইঋও) দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এই খাতের প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধু মূলধন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ওপর নয়, বরং সেই মানবসম্পদের ওপর, যারা প্রতিদিন মাঠে, শাখায়, করপোরেট অফিসে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে সেবা দিচ্ছেন।
কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে চ্যালেঞ্জটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হলো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও ধরে রাখার সীমাবদ্ধতা। আমি একজন নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মানবসম্পদ প্রধান হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখছি— অনেক প্রতিষ্ঠানে ভালো ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম থাকলেও সামগ্রিকভাবে খাতে এখনও প্রস্তুত জনবল কেনার প্রবণতা বেশি, আর দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নের বিনিয়োগ তুলনামূলক কম।
আসলে ব্যাংক ও ঘইঋও উভয়েরই কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ শেষে দেশে মোট ৬১টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, পাশাপাশি ৩৫টির বেশি ঘইঋও সক্রিয়ভাবে বাজারে কাজ করছে। এই খাতে কর্মরত মানবসম্পদের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজারের বেশি, যা ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
কিন্তু একই সময়ে মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান ইধংবষ ওওও-এর ন্যূনতম সীমার নিচে নেমে গেছে। ফলে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো খাতগুলোকে ‘অ-মূল ব্যয়’ মনে করে অগ্রাধিকার কম দেয়া হচ্ছে। অথচ দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব অনেক বেশি গুরুতর।
সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো— অনেক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা উন্নয়নের পরিবর্তে বাজার থেকে ‘প্রস্তুত জনবল’ কেনার প্রবণতা। স্বল্পমেয়াদে এটি সহজ সমাধান মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে দক্ষতার ঘাটতি তৈরি হয়, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানবসম্পদ ধরে রাখার হার কমে যায়। অথচ কর্মীদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করলে তাদের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পায়— এমন প্রমাণিত তথ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান এ দিকটি উপেক্ষা করছে।
এছাড়া অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা গড়ে না তোলার কারণে বাজারে একে অপরের অভিজ্ঞ মানবসম্পদ কিনতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে বেতন-ভাতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং একটি ‘পোচিং কালচার’ তৈরি হয়। একজন দক্ষ কর্মী হারানোর সরাসরি খরচ তার বার্ষিক বেতনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান হলেও আসল ক্ষতি হয় মনোবল ও উৎপাদনশীলতার পতনের মাধ্যমে। নতুন প্রজন্মের কর্মীরা আবার তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়েই চাকরি বদল করতে চায়। ফলে তাদের অভিজ্ঞতাও পরিপক্বতা পায় না এবং দীর্ঘমেয়াদে নেতৃত্ব সংকট তৈরি হয়। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো আবারও বাইরের মানবসম্পদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।
বাংলাদেশে আরেকটি প্রচলিত সংস্কৃতি হলো— ম্যানেজার পরিবর্তনের সঙ্গে দল পরিবর্তন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সিনিয়র কর্মকর্তা নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে তার আগের প্রতিষ্ঠান থেকে পুরো টিমের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে যান। এতে আনুগত্য ব্যক্তি-কেন্দি ক হয়ে পড়ে, প্রতিষ্ঠান-কেন্দি ক নয়। ফলে আগের প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক দক্ষতার ঘাটতি তৈরি হয় এবং কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা জরুরি যে, সব প্রতিষ্ঠান সমান নয়। অনেক ব্যাংক এবং ঘইঋও ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল লার্নিং এবং সাকসেশন প্ল্যানিংয়ের মতো শক্তিশালী উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগ কর্মীদের শুধু দক্ষতাই বাড়ায়নি, বরং তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও জাগ্রত করেছে। মালিকানাবোধ এবং দীর্ঘমেয়াদি আনুগত্যও তৈরি করেছে। সুতরাং চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, ইতিবাচক দৃষ্টান্তও তেমনি রয়েছে, যা অনুসরণযোগ্য।
কিন্তু আজকের দিনে ব্যাংক ও ঘইঋও-এর জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়েছে— প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি। আর্থিক খাতের ডিজিটাল রূপান্তর এখন বাস্তবতা; অও-ভিত্তিক সেবা, ডেটা অ্যানালিটিকস, সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল পণ্য উন্নয়ন এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি আগামী দিনের প্রতিযোগিতার মূল হাতিয়ার। অথচ দক্ষ মানবসম্পদ এখনও পর্যাপ্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অও-চালিত সমাধান তৈরি বা ডিজিটাল ডেটা বিশ্লেষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রযুক্তি গ্রহণের গতি ধীর হচ্ছে, নতুন পণ্য উদ্ভাবন সীমিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং দক্ষতার পাশাপাশি প্রযুক্তি ও ডিজিটাল জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দিয়ে মানবসম্পদ তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।
এই বাস্তবতায় প্রশ্ন ওঠে— আমরা কি কেবল বাজার থেকে মানবসম্পদ কিনে সমস্যার সমাধান করতে পারব, নাকি নিজেদের ভেতরে দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা গড়ে তুলব? অভিজ্ঞতা বলে, প্রস্তুত জনবল কেনা তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও এটি মূল সমস্যার সমাধান নয়। বরং কৌশলগত প্রশিক্ষণ বিনিয়োগ, দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার পথ তৈরি, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কাঠামো, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মতো উদ্যোগই আসল সমাধান হতে পারে। এভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু খরচ কমাতে পারবে না, বরং টেকসই মানবসম্পদ তৈরি করে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।
সবশেষে বলতে চাই, আর্থিক খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি টেকসই স্থিতিশীলতার বিনিয়োগ। দক্ষ জনবল ছাড়া ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কমপ্লায়েন্স কিংবা গ্রাহকসেবা কোনো ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আর্থিক খাতের যেসব প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে টিকে থাকতে চায়, তাদের জন্য এখনই সময় প্রস্তুত জনবল কেনার স্বল্পমেয়াদি মানসিকতা ছেড়ে দিয়ে দক্ষতা গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পথ বেছে নেয়ার।
মানুষে বিনিয়োগ কেবল একটি মানবসম্পদ নীতি নয়, বরং এটি আর্থিক খাতের টেকসই নিরাপত্তা, প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় ভিত্তি।
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মানবসম্পদ প্রধান
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স
 প্রিন্ট করুন
প্রিন্ট করুন

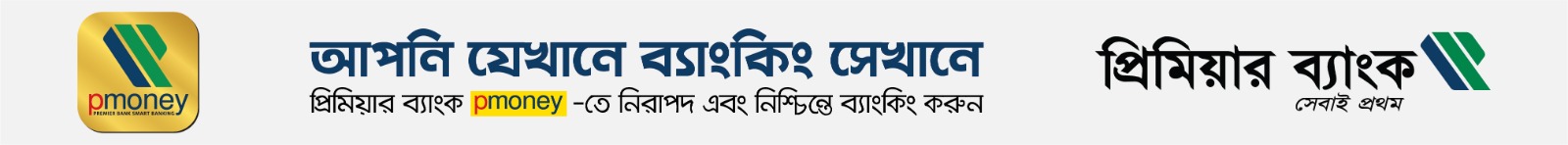










Discussion about this post