ড. মতিউর রহমান : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক সমাজ যে বিভক্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল, তার ধীরে ধীরে ক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয় যখন আমরা ভুল তথ্যের বিস্তার, ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জনপ্রিয়তা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার ঢেউ এবং আবেগ ও পরিচয়ের ভিত্তিতে আখ্যান গ্রহণের মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখি।
এই বৈশ্বিক অবস্থাকে সত্য-পরবর্তী”বা Post-Truth যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক সময়, যেখানে জনমত গঠনে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের চেয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং আবেগের প্রভাব বেশি দেখা যায়। ২০১৬ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ব্রেক্সিট গণভোটের পর এই শব্দটি একাডেমিক ও মূলধারার আলোচনায় গুরুত্ব পেলেও, এর মূল কারণ এবং ফলাফল অনেক বিস্তৃত ও গভীর।
বাংলাদেশের মতো সমাজে, এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটের সমাজতাত্ত্বিক মাত্রা আরও গভীর। কারণ এখানে এটি মিডিয়া একচেটিয়াকরণ, রাজনীতিকৃত জ্ঞান উৎপাদন, শিক্ষাগত ঘাটতি এবং পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে মিশে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।
সত্য-পরবর্তী যুগে জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান বুঝতে হলে, আমাদের প্রথমে এর বৌদ্ধিক ভিত্তিগুলো পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার এবং এমিল ডুর্খেইমের মতো ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানীরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের সামাজিক প্রকৃতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করেছেন। তবে এই ক্ষেত্রটিকে সুনির্দিষ্টভাবে রূপ দেন কার্ল ম্যানহেইম। ১৯২০-এর দশকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আইডিওলজি অ্যান্ড ইউটোপিয়ার মাধ্যমে তিনি যুক্তি দেন যে, সব জ্ঞানই সামাজিকভাবে অবস্থিত এবং তার উৎপাদনের শর্ত দ্বারা গঠিত। ম্যানহেইমের মতে, আদর্শ বা মতাদর্শ হলো সত্যের বিকৃতি নয়, বরং এটি সামাজিক অবস্থানের একটি অনিবার্য ফল।
সত্য-পরবর্তী যুগে যখন জ্ঞান আরও বেশি স্তরবদ্ধ, রাজনীতিকীকরণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে উঠছে, তখন ম্যানহেইমের এই অন্তর্দৃষ্টিগুলো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তার এই ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তথাকথিত সত্য সবসময়ই ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক অবস্থানের জটিল নেটওয়ার্কের মধ্যে নির্মিত ও প্রবাহিত হয়।
বাংলাদেশে বর্তমানে জ্ঞান এমন এক গভীরভাবে বিভক্ত মিডিয়া পরিবেশে উৎপাদিত এবং প্রচারিত হয়, যা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অভূতপূর্ব। সংবাদ এবং মতামতের জন্য ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। একই সঙ্গে এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক গেটকিপিং-এর ঐতিহ্যবাহী কাঠামোকেও ভেঙে দিয়েছে।
ঐতিহ্যবাহী সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা একসময় সত্যের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত, তারা এখন ডিজিটাল নেটওয়ার্কে প্রচারিত অযাচাইকৃত, আবেগপ্রবণ এবং প্রায়শই বানোয়াট তথ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।
উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের সড়ক নিরাপত্তার জন্য ছাত্র বিক্ষোভ বা সাম্প্রতিক ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো জাতীয় সংকটের সময় ভাইরাল হওয়া গুজবগুলো প্রায়ই সরকারি যোগাযোগ চ্যানেলগুলোর চেয়ে দ্রুত জনগণের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। এসব ক্ষেত্রে, ভুল তথ্য অনেক সময় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের কারণ হয়েছে। এর ফলে শাসক প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল জনগণের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক অবিশ্বাসের এক গভীর চিত্র ফুটে উঠেছে।
সত্য-পরবর্তী অবস্থার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান-বিশ্লেষণ বা epistemic fragmentation সমাজের একাধিক, প্রায়শই পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস ব্যবস্থায় বিভক্তি। এই মেরুকরণ কেবল মতামতের ভিন্নতা নয়, বরং বাস্তবতার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণাকে নির্দেশ করে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এটি ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাসের তত্ত্ব অনুযায়ী একটি কার্যকরী জনক্ষেত্রের মূল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। হ্যাবারমাসের মতে, জনক্ষেত্র হলো এমন একটি স্থান যেখানে যুক্তিসঙ্গত-সমালোচনামূলক বিতর্কের মাধ্যমে সাধারণ সত্যের আলোচনা হয়।
আনুগত্য, ধর্মীয় পরিচয় বা শ্রেণি অবস্থান দ্বারা পরিচালিত প্রতিদ্বন্দ্বী মিডিয়া আখ্যানগুলো ভিন্ন ভিন্ন সত্য-জগৎ তৈরি করছে। যেমন, একটি সরকার-পন্থি টেলিভিশন চ্যানেল দেখা একজন নাগরিক সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতা দেখতে পাবেন সেই ব্যক্তির চেয়ে, যিনি সরকারবিরোধী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুসরণ করেন। এই বিভাজন শুধু তথ্যের ভিন্নতা নয়, এটি বাস্তবতার এক ভিন্ন উপলব্ধি তৈরি করে।
এই বিভাজন আরও তীব্রতর হয় যখন আমরা ব্যক্তিগত মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমের ভূমিকা বিবেচনা করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ সম্পৃক্ততা তৈরি করা যায়। এর ফলস্বরূপ, প্রায়শই আবেগপ্রবণ বা চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তুগুলো বেশি অগ্রাধিকার পায়।
বাংলাদেশের ডিজিটাল স্পেস বিশ্লেষণকারী সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে কীভাবে এই অ্যালগরিদমগুলো ইকো চেম্বার তৈরি করতে সাহায্য করে। এই ডিজিটাল পরিবেশগুলোতে ব্যক্তিরা মূলত এমন তথ্যের সংস্পর্শে আসে যা তাদের পূর্ব-বিদ্যমান বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে।
এই ধরনের স্থানে, ভুল তথ্য কেবল সাধারণই নয়, বরং প্রায়শই কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মিথ্যা তথ্য, সাম্প্র্রদায়িক হুমকি বা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ভাইরাল বিস্তার এই ডিজিটাল জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামোগত দুর্বলতারই লক্ষণ।
এই জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভাজনের পরিণতি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থার ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বাংলাদেশে, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়, বিচার বিভাগ এবং সংবাদপত্রের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে, যার পেছনে প্রায়শই বৈধ কারণ বিদ্যমান। দুর্নীতি, রাজনীতিকরণ এবং সেন্সরশিপ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করেছে।
উদাহরণস্বরূপ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে আপসকৃত হিসেবে দেখা হয়, যেখানে অনুষদ নিয়োগ এবং একাডেমিক স্বাধীনতা দলীয় বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি এক ধরনের বৈপরীত্য তৈরি করে: একদিকে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়েও বেশি, অন্যদিকে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐতিহাসিকগতভাবে এটি উৎপাদন এবং প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারাই সন্দেহের চোখে দেখা হয়।
এই সংকটের প্রতিক্রিয়ায়, সমাজবিজ্ঞানীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্প্র্রদায়ের” (epistemic communities) ভূমিকা অন্বেষণ করতে শুরু করেছেন। এই সম্প্রদায়গুলো হলো এমন কিছু অভিনেতার দল, যারা নির্দিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক মানদণ্ড এবং নিয়মাবলির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সম্মিলিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান তৈরির জন্য কাজ করে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাধীন মিডিয়া আউটলেট, আইনি অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, একাডেমিক থিংক ট্যাংক এবং সুশীল সমাজের সংগঠন। যদিও এই গোষ্ঠীগুলো উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে, তারা প্রভাবশালী আখ্যানের বিরুদ্ধে পাল্টা-আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করে।
উদাহরণস্বরূপ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মতো সংস্থাগুলো প্রায়শই গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা শাসন, মানবাধিকার এবং দুর্নীতির বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করে। তবে তাদের কাজগুলো প্রায়শই সত্য-পরবর্তী পরিবেশে উপেক্ষা করা হয় বা নিন্দার শিকার হয়, কারণ এখানে সহজে প্রতিদ্বন্দ্বী সত্য তৈরি করা এবং প্রচার করা সম্ভব।
এই জ্ঞানতাত্ত্বিক যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রে রয়েছে বিশ্বাসের ধারণা। দার্শনিক অনোরা ও’নিল যেমন যুক্তি দিয়েছেন, বিশ্বাস এমন কিছু নয় যা দাবি করা যেতে পারে; এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ধারাবাহিকতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।
জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞানে, বিশ্বাস একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং একটি সম্পর্কীয় উভয় ধরনের গঠন। এটি নির্ধারণ করে যে ব্যক্তিরা কীভাবে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা, উৎসের উদ্দেশ্য এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই জ্ঞানের সারিবদ্ধতাকে বিচার করে।
সত্য-পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, বিশ্বাস প্রায়শই যুক্তির চেয়ে আবেগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয় ভাগ করে নেয়া ব্যক্তিদের ওপর বেশি বিশ্বাস স্থাপন করে, এমনকি যদি তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিতা করে।
এর ফলে কিছু সমাজবিজ্ঞানী যাকে জ্ঞানতাত্ত্বিক উপজাতিবাদ” (epistemic tribalism) বলে অভিহিত করেছেন, তার জন্ম হয়। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে জ্ঞান প্রমাণ বা যুক্তির ভিত্তিতে নয়, বরং দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়।
বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বিস্তারে এই গতিশীলতা বিশেষভাবে স্পষ্ট। এই ধরনের বিশ্বাস, যেমন এনজিওগুলো গোপনে ইসলামকে দুর্বল করার জন্য কাজ করছে, অথবা বিদেশি শক্তি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে— এগুলো স্বচ্ছ তথ্যের অভাবে আরও বৃদ্ধি পায়।
এই আখ্যানগুলো জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়গুলোর জন্য আপাতদৃষ্টিতে সুসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং উপনিবেশবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশি হস্তক্ষেপের সম্মিলিত স্মৃতির সঙ্গে অনুরণিত হয়।
এই ঘটনাগুলো অধ্যয়নকারী সমাজবিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলেন যে, ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো যদিও বস্তুনিষ্ঠভাবে ভিত্তিহীন, সামাজিকভাবে অর্থপূর্ণ। তারা উদ্বেগ, অবিশ্বাস এবং অনুভূত বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, যা সত্য-পরবর্তী সমাজে আস্থা পুনর্গঠনের জন্য সমাধান করা অপরিহার্য।
সত্য-পরবর্তী অবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। জ্ঞানের সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং গণমাধ্যম সাক্ষরতার অপর্যাপ্ততা।
মুখস্থ-ভিত্তিক শিক্ষা সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের তথ্যের উৎসগুলোকে প্রশ্ন করতে, যুক্তি মূল্যায়ন করতে বা পক্ষপাত শনাক্ত করতে শেখায় না। বরং এটি তথ্যের নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, যা ব্যক্তিকে কারসাজির জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে।
সমাজবিজ্ঞানীরা আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা, জ্ঞানতাত্ত্বিক নম্রতা এবং নাগরিক দায়িত্বের ওপর জোর দেয় এমন শিক্ষাগত সংস্কারের আহ্বান জানান। এই ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সত্য-পরবর্তী সমাজের জটিলতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য অপ্রস্তুত থাকবে।
এই প্রসঙ্গে, ফুকোর সত্যের শাসন (regime of truth) তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ফুকোর মতে, সত্য কোনো পরম বিষয় নয়, বরং ক্ষমতা দ্বারা আকৃতির আলোচনামূলক গঠনের মাধ্যমে নির্মিত হয়। যে কোনো মুহূর্তে সত্য হিসেবে যা গণ্য হয়, তা প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা বৈধ জ্ঞানের জন্য প্যারামিটার বা সীমা নির্ধারণ করে।
বাংলাদেশে, সত্যের বর্তমান শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রযন্ত্র, গোঁড়ামি এবং বাজার-চালিত গণমাধ্যম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এই শাসনব্যবস্থাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে প্রায়শই ব্যক্তিগত ঝুঁকি জড়িত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে আইনি নিপীড়ন, সামাজিকভাবে বহিষ্কার, এমনকি সহিংসতা। তবুও বিকল্প জ্ঞান উৎপাদন অব্যাহত থাকে— প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে, গোপন প্রকাশনা, এনক্রিপ্ট করা অনলাইন নেটওয়ার্ক এবং রাস্তার প্রতিবাদে।
এই প্রেক্ষাপটে, প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ধারণা হয়ে ওঠে। যদিও সত্য-পরবর্তী অবস্থাকে প্রায়শই অযৌক্তিকতা বা শূন্যবাদের দিকে অধঃপতনের চিত্র হিসেবে দেখানো হয়, এটি জ্ঞান-উত্তর বিদ্রোহের জন্যও ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে।
বাংলাদেশের যুব-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলো, যেমন- শাহবাগ বিক্ষোভ, ২০১৮ সালের ছাত্র আন্দোলন, অথবা কোটা সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য সাম্প্রতিক ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান— এগুলো দেখায় যে কীভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো বিতর্কিত সত্যের চার পাশে একত্রিত হতে পারে।
এই আন্দোলনগুলো বিকল্প জনক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে সত্য ওপর থেকে নির্দেশিত হয় না বরং নিচ থেকে আলোচনা করা হয়। তারা আধিপত্যবাদী আখ্যানের ফাটলগুলো উন্মোচন করে এবং জ্ঞান-উত্তর কর্তৃত্বের ওপর একচেটিয়া ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে।
বাংলাদেশের সত্য-পরবর্তী রাজনীতির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য, সমাজবিজ্ঞানকে পদ্ধতিগত বহুত্ববাদকে গ্রহণ করতে হবে। মিডিয়া আস্থার ওপর পরিমাণগত জরিপ, জ্ঞান উপলব্ধির ওপর গুণগত সাক্ষাৎকার, অনলাইন আলোচনার ডিজিটাল নৃতাত্ত্বিকতা এবং সংবাদ কাঠামোর আলোচনা বিশ্লেষণ— এইগুলো জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভাঙা ভূখণ্ডের মানচিত্র তৈরির জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার।
অধিকন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের কেবল বিশ্লেষক হিসেবে নয়, বরং জনসাধারণের বুদ্ধিজীবী হিসেবেও কাজ করতে হবে, যারা বৃহত্তর শ্রোতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বেশি সমালোচনামূলক মনোভাব এবং সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে।
সত্য-পরবর্তী যুগে জ্ঞান ও সত্যের সমাজবিজ্ঞান কেবল একটি একাডেমিক অনুশীলন নয়; এটি গণতান্ত্রিক জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে এমন জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটগুলোকে বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হাতিয়ার। বাংলাদেশে, অন্য স্থানের মতোই, এই সংকট বহুমাত্রিক— ঐতিহাসিক অবিশ্বাসের মধ্যে নিহিত, প্রযুক্তিগত বিঘ্ন দ্বারা আকৃতির এবং রাজনৈতিক কারসাজির দ্বারা আরও তীব্রতর। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও পুনর্গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। জ্ঞানকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, সামাজিকভাবে অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করে এমন প্রতিষ্ঠান ও চর্চাগুলোকে শক্তিশালী করে, সমাজ বিভক্ত সত্যের ভঙ্গুর কিন্তু প্রয়োজনীয় ভিত্তি পুনর্গঠন শুরু করতে পারে।
এই প্রচেষ্টায় সমাজবিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে— সত্যের বিচারক হিসেবে নয়, বরং ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুর বিশ্বে জ্ঞানতাত্ত্বিক ন্যায়বিচারের সহায়তাকারী হিসেবে।
গবেষক ও উন্নয়নকর্মী
 প্রিন্ট করুন
প্রিন্ট করুন

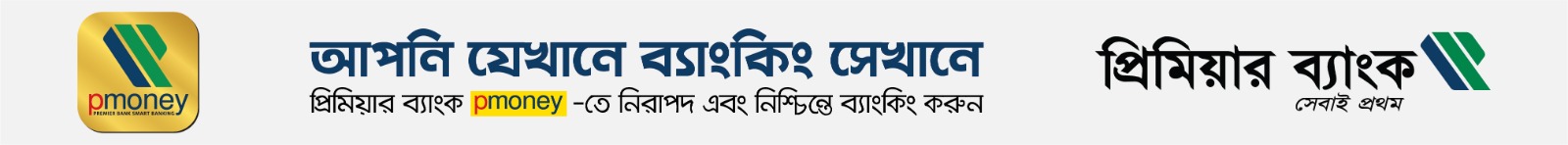












Discussion about this post