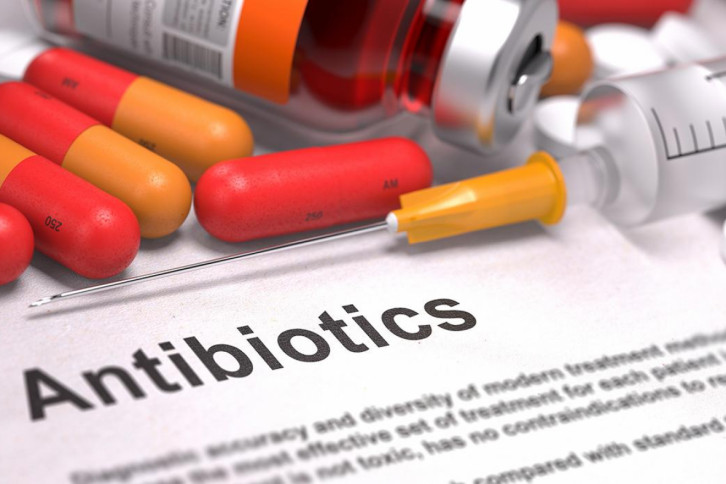মো. আরাফাত রহমান: অ্যান্টিবায়োটিক একধরনের জৈব-রাসায়নিক ওষুধ, যা অণুজীব বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াকে নাশ করে বা বৃদ্ধি রোধ করে। সাধারণত একেক অ্যান্টিবায়োটিক একেক ধরনের প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অণুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে। অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না। প্রকৃতিতেও বহু জীবাণুনাশক আছে, যেগুলোর মধ্যে অনেক দ্রব্যকেই এখনও ওষুধ হিসেবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি, যেমন ব্যাকটেরিওসিন যা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিসৃত ব্যাকটেরিয়াঘাতক প্রোটিন টক্সিন। সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটি দ্বারা ক্ষুদ্র জৈব-রাসায়নিক পদার্থ বোঝায়, বৃহৎ প্রোটিন নয় বা অজৈব-রাসায়নিক অণু নয়।
প্রাকৃতিক উপাদানের যে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে, তা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের অনেক আগে মানুষের জানা ছিল। ১৮৮১ সালে ব্রিটিশ অণুজীব বিজ্ঞানী জন টিন্ডাল ছত্রাকের জীবাণু প্রতিরোধী ভূমিকা লক্ষ করেন। লুই পাস্তুর ও জোবার্ট লক্ষ করেন কিছু অণুজীবের উপস্থিতিতে প্রস্রাবে অ্যানথ্র্রাক্স ব্যাসিলি জš§াতে পারে না। ১৯০১ সালে এমারিখ এবং লও দেখেন, আনথ্রাক্স ব্যাসিলির আক্রমণ থেকে খরগোশকে বাঁচানো সম্ভব যদি সিউডোমোনাস এরুজিনোসা নামক ব্যাকটেরিয়ার তরল আবাদ খরগোশের দেহে প্রবেশ করানো যায়। তারা মনে করেন ব্যাকটেরিয়াটি কোনো উৎসেচক তৈরি করেছে, যা জীবাণুর আক্রমণ থেকে খরগোশকে রক্ষা করছে। তারা এই পদার্থের নাম দেন পাইওসায়ানেজ।
১৯২০ সালে গার্থা ও দাথ কিছু গবেষণা করেন এ-জাতীয় জীবাণুনাশক তৈরি করতে। তারা অ্যাকটিনোমাইসিটিস দ্বারা প্রস্তুত একধরনের রাসায়নিক পদার্থ খুঁজে পান, যার জীবাণুনাশী ক্ষমতা আছে। তারা এর নাম দেন অ্যাকটিনোমাইসিন। কিন্তু কোনো রোগের প্রতিরোধে এই পদার্থ পরবর্তীকালে ব্যবহার করা হয়নি। এ-জাতীয় আবিষ্কারের পরও ১৯২৯ সালের আগে অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ শুরু হয়নি। প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ১৯২৭ সালে লন্ডনের সেন্ট মেরি হাসপাতালে কর্মরত অণুজীব বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন। ফ্লেমিং তার এক পরীক্ষার সময় লক্ষ করেন জমাট আবাদ মাধ্যমে ছত্রাকের উপস্থিতিতে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস নামক ব্যাকটেরিয়া জš§াতে পারে না।
আবাদ মাধ্যমে ছত্রাকের উপস্থিতি কাম্য ছিল না, তবে পরীক্ষাকালে কোনো অজানা ত্রুটির কারণে ছত্রাক আবাদ মাধ্যমে চলে এসেছিল। ফ্লেমিং তখন ওই ছত্রাকের প্রজাতি চিহ্নিত করতে ও তার জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করতে আগ্রহী হন। ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম। ফলে ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম দ্বারা নিসৃত ওই পদার্থের নাম দেন পেনিসিলিন। পেনিসিলিয়াম একা নয়, অন্য আরেক ধরনের ছত্রাক প্রজাতি, যেমন অ্যাস্পারজিলাসও পেনিসিলিন তৈরি করতে পারে। ফ্লেমিং যে ছত্রাক পেয়েছিলেন তা ২ একক/মিলিলিটার পেনিসিলিন তৈরি করত, কিন্তু কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা প্রায় ৯০০ একক/মিলিলিটার পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার একক/মিলিলিটার পেনিসিলিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। রেনে ডিউবস গ্রামিসিডিন ও টাইরসিডিন আবিষ্কার করেন, যা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ওপর কাজ করে। বর্তমানে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু ক্লোরামফেনিকলের রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।
১৯৪১ সালের ১২ ফেব্রুয়াারি প্রথম পেনিসিলিন মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয়। অক্সফোর্ডের এক পুলিশ কর্মকর্তা স্ট্যাফাইলোকক্কাস দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। পেনিসিলিনের প্রয়োগে তার অবস্থার নাটকীয় উন্নতি ঘটে। কিন্তু পাঁচ দিন পর পেনিসিলিয়ামের সরবরাহ শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মারা যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ক্ষত সারাতে পেনিসিলিনের ব্যাপক চাহিদা প্রথম সৃষ্টি হয়। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফ্লেমিংয়ের সেই ভুলের কারণে পাওয়া ছত্রাক দিয়ে এক ‘জাদুকরী ওষুধ’ তৈরি করতে থাকে, যা অসংখ্য জীবন বাঁচায়। ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং, আর্নেস্ট চেইন ও ফ্লোরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
কিছু ব্যাকটেরিয়া কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, অন্যদিকে অন্য কিছু ব্যাকটেরিয়া ওই একই অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা আক্রান্ত হয়। এমনকি কিছু ব্যাকটেরিয়া যে কিনা একটি অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সেও #পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে এমন সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, যার ফলে ব্যাকটেরিয়াটি ওই অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী হয়ে ওঠে; যেমন ব্যাকটেরিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে এমন উৎসেচক তৈরি করতে পারে, যা ওই অ্যান্টিবায়োটিকটি বিনষ্ট বা পরিবর্তন করে অকেজো করে দেয়। যেমন: ক্লোরামফেনিকল অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ। একক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ক্যাপস্যুল ও দলবদ্ধ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বায়োফিল্ম; অ্যান্টিবায়োটিক কোষঝিল্লির বাইরে পাম্প দ্বারা বহিষ্কৃত হয়; অ্যান্টিবায়োটিকের লক্ষ্যবস্তুর গঠন পরিবর্তিত হওয়া; লক্ষ্যবস্তুর জিনগত মিউটেশন দ্বারা অনাক্রম্যতা; অন্য উৎসেচক প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত অনাক্রম্যতা; অ্যান্টিবায়োটিকটি যে পদার্থের সংশ্লেষণের বা বিয়োজনের জৈব-রাসায়নিক গতিপথে বাধা দেয়, কোষ ঠিক একই কাজের জন্য অন্য জৈব-রাসায়নিক গতিপথ ব্যবহার করতে পারে।
যে কোনো ব্যাকটেরিয়ার পপুলেশনে একটিমাত্র ব্যাকটেরিয়ার পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের ফলে ওই ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হতে পারে। এই মিউটেশনের প্রাথমিক হার খুব কম; প্রায় একটি মিউটেশন ঘটে প্রতি কয়েক লাখ কোষে। তবে একটি ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী হওয়ার সম্ভাব্যতা অনেক অংশে বেড়ে যায়, যখন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন গ্রহণ করে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াতে তার নিজ ক্রোমসোমস্থ ডিএনএ’র বাইরে আরও কিছু বংশগতির উপাদান থাকে, যাদের কে বলা হয় প্লাজমিড। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী জিনগুলো এসব প্লাজমিড বহন করে। একটি ব্যাকটেরিয়া এই প্লাজমিড বা প্লাজমিডের প্রতিলিপি অন্য ব্যাকটেরিয়ায় স্থানান্তর করতে পারে। যে পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া এই কাজটি করে, তাকে বলা হয় কনজুগেশন।
তাছাড়া প্রায়ই ব্যাকটেরিযার ক্রোমোসোমে বা প্লাজমিডে ট্রান্সপোজন নামে এক বিশেষ অংশ থাকে, যা কিনা অ্যান্টিবায়েটিক-রোধী জিন বহন করে। ট্রান্সপোজন এক ক্রোমোসোম থেকে অন্য ক্রোমোসোমে বা ক্রোমোসোম থেকে প্লাজমিডে যেতে পারে। এর ফলে অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী জিনের বা তার প্রতিলিপির স্থানান্তর ঘটে। অনুন্নত অঞ্চলে অ্যান্টিবায়োটিকের সবচেয়ে অপব্যবহার ঘটে। এসব স্থানে বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে দক্ষ লোকের অভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রায় সর্বত্রই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করা হয়। এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাত্র আট শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তারের উপদেশে বিক্রি করা হয়। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই সাধারণ মাথাব্যথা, পেটব্যথা, জ্বর প্রভৃতির জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।
অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বলার সময় ওই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রোগীর শরীরের ব্যাকটেরিয়া আগেই প্রতিরোধী হয়ে গেছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হয় না। আবার অনেক সময় রোগের শুরুতেই অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের উপদেশ দেয়া হয়, কিন্তু হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া রোগ নিরাময় সম্ভব ছিল। এসব কারণই অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী ব্যাকটেরিয়ার টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। উন্নত বিশ্বেও এ সমস্যা বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সিডিসির এক জরিপে দেখা গেছে, সেখানে ডাক্তাদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপসনে কানের সংক্রমণের জন্য ৩০ শতাংশ, সাধারাণ ঠাণ্ডার জন্য ১০ শতাংশ এবং গলাব্যথার জন্য ৫০ শতাংশ ব্যবস্থাপত্র অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া যারা হাসপাতালে কাজ করে, তাদের মধ্যে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি থাকে বেশি।
অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, অন্তত যেসব ক্ষেত্রে খুব কম অ্যান্টিবায়োটিক দরকার বা একেবারেই দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক শুধু অণুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে; অর্থাৎ যেসব রোগ অণুজীবের সংক্রমণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেসব রোগ নিরাময়ে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে কোনো লাভ হবে না। বরং দেহে ওই বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার ঘটবে এবং পরবর্তীকালে কোনো রোগ ওই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ঘটে থাকলে তখন রোগ নিরাময়ে ওই অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসবে না। ভাইরাসঘটিত রোগে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসে না, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বিরুদ্ধে কাজ করে।
অ্যান্টিবায়োটিক বেশি খাওয়াও ক্ষতিকারক, পাশাপাশি কম খাওয়াও উচিত নয়। কম খেলে ব্যাকটেরিয়া যদি সম্পূর্ণভাবে না মরে যায়, তাতে আবার সংক্রমণ দেখা দেবে। বেশি খেলে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রে অনেক উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, সেগুলোও মরে যায়। এর ফলে বেশ কিছু রোগ দেখা দেয়। একইসঙ্গে অপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো তখন বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন আমাদের যে সাধারণ হাঁচি-কাশিজাতীয় ঠাণ্ডা লাগা, সেটা মূলত ভাইরাসঘটিত করোনাভাইরাস, রাইনোভাইরাস প্রভৃতি এজন্য দায়ী। এগুলোর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। ঠিক যে-ই অ্যান্টিবায়োটিক দরকার, সে-ই অ্যান্টিবায়োটিকই প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করতে হবে।
ডাক্তার যখন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে পরামর্শ দেবে, তখন ডাক্তারের পরামর্শমতো সঠিক সময়ের ব্যবধানে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক সময় পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হবে। যক্ষ্মার মতো রোগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দুই বা ততোধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এতে অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা অনেকাংশে কমে যায়। যখনই কোনো কোনো ব্যক্তির দেহের ব্যাকটেরিয়া একটি বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক-রোধী হয়ে যায়, তখনই যত শিগগির সম্ভব অন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত। ওষুধ দেয়ার আগে জেনে নেয়া উচিত, সেই ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না। ওষুধ দেয়ার আগে স্কিন টেস্ট করে নেয়া উচিত। যদি রি-অ্যাকশন দেখা দেয়, তাহলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। যথেচ্ছ পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। রোগীর লিভার ও কিডনির অবস্থা বুঝে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া উচিত।
সহকারী কর্মকর্তা
ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট
সার্ভিসেস বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়