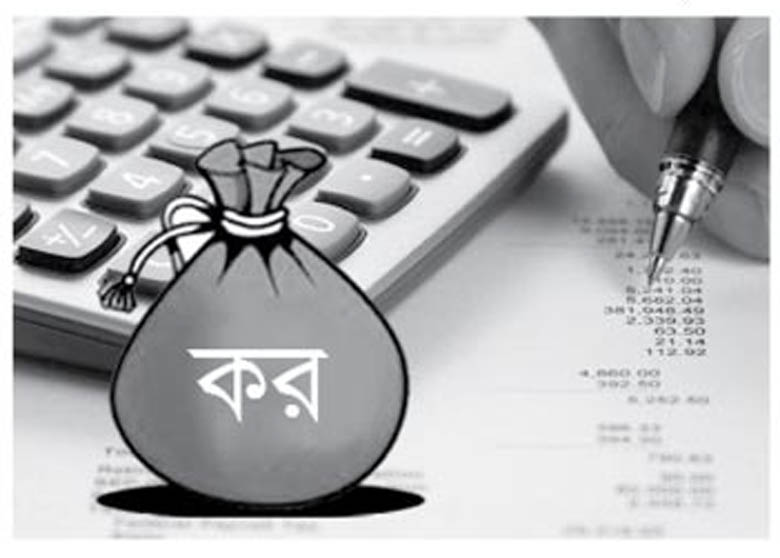বাংলাদেশে কেনাকাটার ক্ষেত্রে কর না দেয়ার প্রবণতা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই কর ফাঁকি দিয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয় করেন, যা দেশের অর্থনীতিতে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে। কর ফাঁকির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী কী ক্ষতি হচ্ছে এবং এর প্রতিকার কী তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় কিন্তু কোনো কার্যকর প্রতিকার হয় না। আসলে কর ফাঁকি এক ধরনের ভদ্রবেশী অপরাধ। সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, করপোরেট সংস্থা বা সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানি কর্তৃক তাদের পেশাগত কাজের প্রক্রিয়ায় এমন কিছু অপরাধমূলক কাজ করে থাকে; যা ভদ্রবেশী অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন আয়কর ফাঁকি, ভ্যাট জালিয়াতি, আমদানি শুল্ক কম পরিশোধ, আবগারি শুল্ক যথাযথভাবে পরিশোধ না করা ইত্যাদি। এই ভদ্রবেশী অপরাধের প্রভাব সমাজে মারাত্মক।
সম্প্রতি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে (সিপিডি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলছে, বাংলাদেশে কর ফাঁকির কারণে সরকার ২০২৩ সালে (২০২২-২৩ অর্থবছর) আনুমানিক ২ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে এবং ২০১২ সালে কর ফাঁকির এই পরিমাণ ছিল ৯৬ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ১১ বছরে দেশে কর ফাঁকির পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। সিপিডি ‘করপোরেট আয়কর সংস্কার ও কর ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলছে, একদিকে বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে অনেক প্রতিষ্ঠান কর দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ছে। গবেষণায় অংশ নেয়া ৪৫ শতাংশ কোম্পানি জানিয়েছে, করপোরেট কর দেয়ার সময় কর কর্মকর্তারা ঘুষ চেয়েছেন। এছাড়া ৮২ শতাংশ কোম্পানি বিদ্যমান কর হার অন্যায্য বলে দাবি করেছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১১ সালের পর থেকে দেশে কর ফাঁকি আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। ২০১২ সালে কর ফাঁকির পরিমাণ ছিল ৯৬ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা, যা ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকায়। সিপিডি বলছে, কর ফাঁকির মূল কারণ হচ্ছে উচ্চ করহার, দুর্বল নজরদারি, জটিল আইন-কানুন ও কর ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘কর ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক কর ফাঁকি সৎ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করে এবং আইনের প্রতি অনুগত নাগরিকদের ওপর করের বোঝা বাড়িয়ে দেয়।’
পৃথিবীর সব দেশেই কর ফাঁকি একটি বড় সমস্যা। উন্নত দেশগুলোয় কঠোর আইনকানুন, এর যথাযথ প্রয়োগ ও সচেতনতার কারণে কর ফাঁকি যথেষ্ট রোধ করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে কর ফাঁকি একটি বড় সমস্যা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় করের ক্ষেত্রেই ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে। রাজস্ব বোর্ডকে প্রতি বছর একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সেটা না হলে তাদের কার্যক্রম গতিশীল হয় না। অর্থনীতিবিদরা বলেন, কর ফাঁকির কারণে অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ভ্যাটের যে কালেকশন হয় সেটার পুরোটা সরকারের কোষাগারে জমা হয় না। আবার প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা ব্যক্তি করে যে ধরনের নজরদারি, খবরদারি করার কথা, বিশেষ করে করের আওতা বাড়ানো, ডিজিটালাইজেশনের আওতা বাড়ানো, সহজীকরণ করাÑএসব জায়গায় সরকারের আশানুরূপ নজরদারি নেই।
সিপিডি করপোরেট আয়কর নিয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয়Ñএমন মোট ১২৩টি কোম্পানির তথ্য নিয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও চামড়াÑএই পাঁচটি খাতের ব্যবসায়ী নেতাদের মতামত নেয়া হয়েছে এবং গত বছরের ডিসেম্বর মাসে জরিপটি পরিচালিত হয়েছে। সিপিডির মতে, ২০২৩ সালে আনুমানিক ২ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা কর ফাঁকি ঘটেছে এবং এর মধ্যে করপোরেট কর ফাঁকির পরিমাণই অর্ধেক বা ৫০ শতাংশ; সেই হিসাবে ২০২৩ সালে আনুমানিক ১ লাখ ১৩ হাজার ১১৮ কোটি টাকা করপোরেট কর ফাঁকি দেয়া হয়েছে।
কর ফাঁকির কারণে সরকারের যে ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেÑপ্রথমত, কর হলো সরকারের প্রধান আয়ের উৎস। যখন জনগণ কর প্রদান থেকে বিরত থাকে, তখন সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সরকারের পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে হয় মূলত কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে। কর ফাঁকি দেয়ার ফলে এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয়ত, যেসব ব্যবসায়ী কর প্রদান করেন না, তারা কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের তুলনায় অসাধু প্রতিযোগিতার সুযোগ পান। এর ফলে সৎ ব্যবসায়ীরা বাজারে টিকতে কষ্ট পায় এবং অনেক সময় ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। চতুর্থত, কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর ফলে গরিব ও সাধারণ জনগণ আরও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক সেবা প্রদান ও পুনর্বণ্টনের সুযোগ হারিয়ে যায়। পঞ্চমত, একটি দেশের অর্থনৈতিক সুশাসন ও স্বচ্ছতা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর ফাঁকির উচ্চ হার দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি করে।
অন্যদিকে, কর ফাঁকি রোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেÑপ্রথমত, কর ফাঁকির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো উচিত। মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে কর প্রদান করতে উৎসাহিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, কর প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অনলাইনে কর প্রদানের সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে জনগণকে কর দিতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, কর নিরীক্ষা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। যারা কর ফাঁকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নেয়। চতুর্থত, জনগণকে বোঝাতে হবে যে, কর প্রদানের মাধ্যমে তারা সরাসরি সরকারি সেবা ও সুবিধা পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন হলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর দিতে আগ্রহী হবে। পঞ্চমত, যারা নিয়মিত কর প্রদান করেন, তাদের জন্য প্রণোদনা ও সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। যেমনÑকর প্রদানে ছাড়, পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান করা যেতে পারে।
অনেকেরই বাংলাদেশের দেশের অন্যতম সেরা করদাতা কাউছ মিয়ার কথা জানা আছে। তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে সেলিব্রিটি নন, তার চেয়ে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আছে কিন্তু হাকিমপুরী জর্দার স্বত্বাধিকারী এই ব্যবসায়ী তার জীবদ্দশায় ২০ বার সেরা করদাতা নির্বাচিত হন। দেখা যাচ্ছে, এনবিআর যখন সেরা করদাতা পুরস্কার দেয়, তখন সব সেলিব্রিটি ও বড় ব্যবসায়ীকে পেছনে ফেলে তিনিই সেরা করদাতা হন। এক্ষেত্রে তাঁর সততা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই গৌরব ও সম্মানের। একইসাথে যারা বছরের পর বছর কর ফাঁকি দেয় তাদের জন্য লজ্জার।
অন্যদিকে, ছাগলকাণ্ডে আলোচিত এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমানের কথা অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে। গত বছর কোরবানির ঈদের আগে মতিউর রহমানের ছেলে অর্ণব ১৫ লাখ টাকায় ছাগল কিনে আলোচনায় আসেন। এরপর বেরিয়ে আসে তার কোটি টাকার গাড়ি ও আভিজাত জীবনযাপনের নানা তথ্য। ধীরে ধীরে গণমাধ্যমে উঠে আসে মতিউর রহমানের স্ত্রী, ছেলে ও কন্যাদের সম্পদের নানা তথ্য এবং তাকে এরপর ওএসডি করা হয়। ইতোমধ্যে দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং সম্প্রতি তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া অতিসম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একজন সদস্য এবং ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য ও সাবেক কর কমিশনারকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই আয়কর জোন-৫-এ কর্মরত থাকার সময় করদাতাদের সাথে যোগসাজশ করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। করদাতাদের সাথে যোগসাজশ করে এ ধরনের কর ফাঁকির ঘটনা বহু ঘটলেও এর খুব কমই জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। এ ধরনের অসৎ কর্মকর্তাদের জন্য করদাতারা একদিকে কর ফাঁকি দিকে উৎসাহিত হয় এবং সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।
সিপিডির গবেষণা বলছে, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় থাকা বাংলাদেশের জন্য এই পরিস্থিতি বড় চ্যালেঞ্জ। এলডিসি উত্তরণের পর বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার ফলে কর ফাঁকি ও কর পরিহারের ঝুঁকিও বাড়বে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিপিডি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর ব্যবস্থার ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন ও নীতিগত সংস্কারের সুপারিশ করেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আরও বলছে, কর ফাঁকি ছাড়াও প্রণোদনা ও কর ছাড়ের কারণে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে। বিনিয়োগের কথা বলে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর ছাড় দেয়া হচ্ছে। এগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। প্রণোদনা বা কর ছাড় বিনিয়োগের ভিত্তি হতে পারে না।
আসলে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বড় বাধা হচ্ছে লোকবল সংকট ও অসৎ লোকবল। এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। মোটকথা জনবল, টেকনোলজিক্যাল ক্যাপাসিটি, ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলÑএগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরেকটি বড় একটি সমস্যা হচ্ছে অটোমেশন। আমরা অনেক বছর ধরেই অটোমেশনের কথা শুনে আসছি। বিভিন্ন সময়ে ভ্যাটের অটোমেশন, ইনকাম ট্যাক্সের অটোমেশন, কাস্টমসের অটোমেশনসহ অসংখ্য প্রকল্প এলো আর গেল। কিন্তু একটি পরিপূর্ণ অটোমেশন সেবা পাইনি; যার কারণে কর ফাঁকি রোধ করা যাচ্ছে না।
সার্বিকভাবে, কর ফাঁকির প্রবণতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুতর ক্ষতি করছে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োজন। কর প্রদান করে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা আমাদের সবার দায়িত্ব।
লেখক: ব্যাংকার ও কলাম লেখক