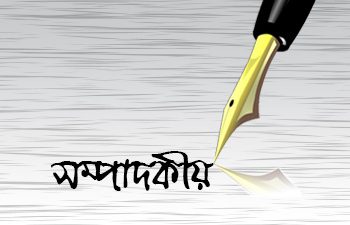দেশে গত মার্চে রেমিট্যান্স এসেছে ৩২৯ কোটি মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগেও অর্থনীতির সূচকগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আমরা গভীর উদ্বেগে ছিলাম। তখন রিজার্ভ কমে যাচ্ছিল, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, আর প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ছিল আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী। ৩২৯ সংখ্যাটি নিছক একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি একটি বার্তা, দেশের বাইরে থাকা প্রবাসীরা আবারও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, বৈধপথে পাঠানো টাকাও ঠিকঠাক পৌঁছায় এবং দেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে নিরাপদ হাতে আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৭৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের (২০২৩-২৪) একই সময়কালের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। শুধু ফেব্রুয়ারিতেই এসেছে ২২০ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১০ কোটি ডলার এবং ডিসেম্বরেও একই ধারায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ২০০ কোটির ঘরে। এই আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনের মূল কথাটি হলো, সরকার বদলেছে, শাসনের ধরন বদলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, আস্থার জায়গা বদলেছে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে মুক্ত, প্রশাসনিকভাবে উদার এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দৃঢ়। যে প্রশাসন জনতার কথায় কান দেয়, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং জাতীয় স্বার্থে কাজ করে, তাতে মানুষ বিশ্বাস রাখবেই।
সরকার প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহ দিতে ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা চালু রেখেছে। মোবাইল অ্যাপভিত্তিক রেমিট্যান্স সিস্টেমে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, হুন্ডি বন্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা এবং প্রবাসী কূটনৈতিক মিশনগুলোর দায়িত্বশীলতা, এসব মিলেই তৈরি হয়েছে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। প্রবাসীরা এখন জানেন, তারা যে ডলার পাঠাচ্ছেন, তা দেশের কাজে লাগছে, মাঝপথে হারিয়ে যাচ্ছে না।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, শুধু রেমিট্যান্স প্রবাহ নয়, এই প্রবণতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যও আশাব্যঞ্জক। রিজার্ভ ঘাটতি কমেছে, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়েছে এবং বৈদেশিক লেনদেনের চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এর অর্থ, প্রবাসী আয়ের এই ধারা অর্থনীতির রক্তপ্রবাহের মতো কাজ করছে। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। এই আস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে বৈধ শ্রমবাজার আরও প্রসারিত করতে হবে, প্রবাসী কল্যাণব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং রেমিট্যান্সের ব্যবহারকে উৎপাদনমুখী খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তা না হলে এই অর্থ কেবল ভোগব্যয়ের পেছনে ব্যয় হয়ে যাবে, দেশের কাঠামোগত উন্নয়নে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলবে না।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রবাসীদের এই আস্থা যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে শুধু রেমিট্যান্স নয়, দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক সূচকেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে। এই আস্থা আর স্থিতিশীলতার যুগ যেন দীর্ঘায়িত হয়, সেটাই এখন প্রত্যাশা।
চোখের শুষ্কতা কেন বাড়ছে
আজকাল ড্রাই আই বা চোখের শুষ্কতার সমস্যা বাড়ছে। বিশেষ করে যারা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন বা দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখেন বা মুঠোফোন ব্যবহার করেন, এমন ব্যক্তিদের অনেকেই ড্রাই আইয়ের সমস্যায় পড়েন। এসি বা ফ্যানের সরাসরি বাতাস, ঘরে কম আর্দ্রতা ও বায়ুদূষণের কারণেও ড্রাই আই হতে পারে। ডায়াবেটিস, সিজোগ্রেন সিনড্রোম ও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসের মতো পরিস্থিতিও চোখের শুষ্কতার জন্য দায়ী। কিছু ওষুধ যেমন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি চোখের শুষ্কতা ঘটাতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও মেনোপজের পর নারীদের চোখ শুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখের প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি। এই পানি শুকিয়ে যাওয়া অনেক রোগের লক্ষণ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ পানির উৎপাদন কিছুটা কমে। ৫০ বছর বয়সের পর পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়।
কীভাবে বুঝবেন: চোখে কাঁটার মতো লাগা, কিছু বিঁধে থাকার মতো অনুভূতি ও চোখ দিয়ে পানি পড়া চোখের শুষ্কতার পূর্বলক্ষণ। এ কারণে মাথাব্যথা থেকে জ্বর ও নাক বন্ধ থাকার রোগও হয়ে থাকে। বারবার মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখে পর্যাপ্ত লালাগ্রন্থি না থাকা বা কথা জড়িয়ে যাওয়ার সমস্যাও থাকতে পারে।
চিকিৎসা কী: চিকিৎসক শুরুতেই চোখের পানির গুণগত মান, পরিমাণ ও গঠনসম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা করবেন। ভিটামিন ‘এ’-এর ব্যবহার এবং কারণ অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করলে চোখের শুষ্কতা দূর করা যায়। সব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম চোখের পানি ব্যবহার করা যায়। মিথাইল সেলুলোজ, সফট কন্ট্যাক্ট লেন্স ও প্যারোটিভ ডাক্ট প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেও চোখের শুষ্কতার প্রতিকার করা যায়।
ঘরোয়া প্রতিকার কী: প্রচুর পানি পান করতে হবে। নিয়মিত চোখের ব্যায়াম করা যায়। খাদ্যতালিকায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার রাখুন। একনাগাড়ে না তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলা ভালো। মিনিটে ১৫-৩০ বার চোখের পাতা পিটপিট করা প্রয়োজন। ২০ সেকেন্ডের বেশি চোখ খোলা রাখা উচিত নয়। ২০ মিনিট পরপর মনিটর থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ সরাতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার সময় চোখে আই প্রোটেক্টর স্পেকটিক্যাল ব্যবহার করা ভালো। বাইরে বেরোলে ভালো মানের রোদচশমা পরার অভ্যাস করুন। হালকা গরম পানিতে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ডুবিয়ে সেই কাপড় নিংড়ে নিয়ে চোখের ওপর পাঁচ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা চাপে চোখের ওপরের ও নিচের পাতায় কাপড়টা মালিশ করলে চোখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতে চোখের আর্দ্রতাও বাড়বে। পরিষ্কার তুলায় নারকেল তেল দিয়ে চোখের ওপর ১৫ মিনিট রাখতে পারেন। দিনে বেশ কয়েকবার এটা করা যায়। পরিষ্কার টিস্যুতে অ্যালোভেরা জেল নিয়ে চোখের নিচের পাতায় আলতো হাতে মালিশ করুন। ১০ মিনিট পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন। এটা দিনে দুবার করতে পারেন।
অধ্যাপক ডা. সৈয়দ এ কে আজাদ
চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ফ্যাকো সার্জন বিভাগীয় প্রধান
আল-রাজী হাসপাতাল, ফার্মগেট, ঢাকা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস আজ। ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে তার জš§। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা, পরে হুগলির ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের যে দুজন ছাত্র বিএ পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাদের একজন। তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিম্ন নির্বাহী চাকরিতে (সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস) যোগ দেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করেন। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাকে ১৮৯১ সালে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি প্রদান করে।
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসেবে মফস্বলে চাকরিরত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলার জনগণের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংসর্গ এবং তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া থেকে তিনি তার উপন্যাসের চরিত্র গ্রহণ করেন।
চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা রচনা করেন। ১৮৮৭ সালের মধ্যে তার অন্যান্য গদ্য রচনাসহ মোট ১৪টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ থেকে বঙ্কিমমনীষা রাজনীতি ও ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেসময় তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। আনন্দমঠ (১৮৮২) সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। বাংলা উপন্যাস ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাময়িকী সাহিত্যের প্রসারেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তার বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন: রাজসিংহ (১৮৮২) এবং সীতারাম (১৮৮৮)। কোনো কোনোটিতে আবার ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধেও হিন্দুজাতির বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন: দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ।
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মধ্যপন্থি রাজনৈতিক নেতারা প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী সেøাগানে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু স্বদেশী যুগের যুবসমাজের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা এবং তার মতাদর্শে যুবসমাজের মধ্যে যে উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল, তা কংগ্রেসকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে এবং একটি জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হতে প্রভাবিত করে। এরপর কংগ্রেস তার জাতীয় রাজনীতির সেøাগান হিসেবে ‘বন্দে মাতরম্’কে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তা ব্যবহƒত হতে থাকে। অতীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্যব্যক্তিত্ব হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের আবির্ভাব পর্যন্ত সবার কাছে, এমনকি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কাছেও সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন। ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [সংগৃহীত]
গাজা: ক্রমবর্ধমান মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট
গাজী তারেক আজিজ
গাজা উপত্যকা ফিলিস্তিনের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, যা দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি দখলদারত্ব, অবরোধ ও সংঘাতের শিকার। ইসরায়েল ও মিসরের অবরোধের ফলে গাজার অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সাধারণ জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত এক দশকে গাজা উপত্যকা হয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম আলোচনার কেন্দ্র, যা ইসরায়েলি বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়ে মানবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। ইসরায়েল-হামাস সংঘাত নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও শক্তির রাজনীতিকে। গাজার বর্তমান অবস্থা কেবল একটি ভূখণ্ডের সংকট নয়, বরং এটি আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক মূল্যবোধের একটি প্রতিচ্ছবি।
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, নাকি নতুন অধ্যায়: গাজার সংকট নতুন নয়। ২০০৭ সালে হামাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর থেকে এই ভূখণ্ড কার্যত এক বৃহৎ খোলা কারাগারে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েল ও মিসরের অবরোধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়েন, ও দারিদ্র্যের মধ্যে বন্দি প্রায় ২৩ লাখ মানুষ প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়। বলা বা ব্যাখ্যা করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে যায় সুস্থ স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষের।
তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সহিংসতা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ। হামাসের হামলায় ইসরায়েলের বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল পাল্টা আক্রমণ শুরু করে গাজায়। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ নিহত, লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত এবং অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে এমন জনমানবহীন ধ্বংসযজ্ঞ কল্পনাও করা কঠিন, যা চলছে বিরামহীনভাবে!
সাম্প্রতিক সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়: ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। এই সংঘাতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা যায়, যার মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। এ ছাড়া ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬২ জন আহত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ১৫ প্যালেস্টিনীয় স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন হামলার ভিডিও ধারণ করেছিলেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। যদিও ইসরায়েল এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও দ্বৈত মানদণ্ড: গাজার বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় যে দ্বৈত মানদণ্ড রয়েছে, তা আজ আর অজানা নয়। পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ শুরুতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেও গাজার বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার তীব্রতা বাড়ে। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যদের ভূমিকায় দেখা গেছে কৌশলগত দ্বিধাÑএকদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা, যা কেবলই মোড়লি রাষ্ট্রের অবিমৃষ্যকারী বৈ আর কিছু কি? এই দ্বৈত মানদণ্ড বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছেÑইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতায় যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ, গাজার ক্ষেত্রে সেই নৈতিক জোর কোথায় হারিয়ে যায়? কেনই বা বিশ্ববিবেক এতটা নীরব থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে, তাও কি ভাববার বিষয় নয়? নাকি এভাবেই ধ্বংস করে দেয়া হবে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও নাগরিকদের? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, আরব বিশ্বও কেন মৌনব্রত পালন করছে?
আরব বিশ্বের মৌনতা ও বাস্তবতা: আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও জনমনে প্রবল ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখা গেছে, অনেক সরকার কৌশলগতভাবে নীরব থেকেছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে হাঁটছিল এবং গাজার যুদ্ধ সেই প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুললেও পুরোপুরি থামায়নি। আদতে থামানোর কোনো উদ্যোগও লক্ষণীয় ছিল বলেও মনে হচ্ছে না! উপরন্তু তারা যেন ‘মামা শ্বশুরের সামনে ভাগনে বউয়ের ভূমিকায়’ থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরে জানাবে ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে!
মিসরের ভূমিকাও সমালোচিত। রাফা সীমান্ত অল্প সময়ের জন্য খুললেও অধিকাংশ সময়ই তা বন্ধ ছিল। মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা, আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থান না দেওয়াÑসবই প্রমাণ করে, গাজা শুধু ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট নয়, এটি আরব বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। এতে বোঝা যায়, মানবিক সংকটের ঊর্ধ্বে একেক দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থই যার যার কাছে বড়, যা তাদের আচরণে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
হামাসÑপ্রতিরোধ না সন্ত্রাস: হামাসের ভূমিকাও এ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেদের ‘প্রতিরোধ আন্দোলন’ হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ করে হামলা চালানোর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের সন্ত্রাসী তকমা অটুট রয়েছে। এর ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নটিও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলকে একটি ‘নিরাপত্তা হুমকি’ উপস্থাপন করতে সহায়তা করে, যার ওপর ভিত্তি করে ইসরায়েল তার আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে আমেরিকা ও মিত্র শক্তির।
তবে হামাসের উত্থানের মূল কারণগুলো হলোÑইসরায়েলি দখলদারত্ব, রাজনৈতিক দমন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। সেগুলো বিশ্লেষণে না এনে শুধু প্রতিক্রিয়াকে দোষারোপ করাই কি যথাযথ? কার্যত যা-ই হোক একেবারে সেসবও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তারপরও ভুক্তভোগী গাজা তথা ফিলিস্তিনের বেসামরিক জনগণ।
মিডিয়া ও তথ্য যুদ্ধ: গাজার যুদ্ধ আরেকটি বড় মাত্রা পেয়েছে তথ্যমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পশ্চিমা মূলধারার সংবাদমাধ্যমে অনেক সময়ই পক্ষপাতদুষ্টতা চোখে পড়ে, যেখানে ইসরায়েলের প্রাণহানিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর গাজার গণহত্যা তুলনামূলকভাবে গৌণ করে উপস্থাপন করা হয়। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের জোয়ার দেখা গেছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজšে§র মধ্যে। যে কোনো ঘটনাই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। এতে করে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যেভাবেই প্রচার করুক না কেন, সুরের যেমন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না, তেমনই কান্নার বা চোখের জলেরও আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না, যা দেখেই মানুষ বুঝে নিতে পারে। কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয় না।
এটি প্রমাণ করে, তথ্য এখন আর একমুখী নয়। মানুষ নিজেরাই ছবি, ভিডিও ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরছে। যদিও ইসরায়েল বারবার গাজায় ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তথ্যপ্রবাহ থামানোর চেষ্টা করেছে, তা পুরোপুরি সফল হয়নি, যা ইসরায়েলের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক উš§ত্ততা প্রকাশে বিঘ্ন না ঘটিয়ে আরও সহায়ক হয়। এতে বিশ্ববাসীর নজর এড়িয়ে যায়নি।
সামনে কী: গাজার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে বিশ্ব। যদি যুদ্ধ থেমেও যায়, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এটি কেবল অস্থায়ী বিরতি হবে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান, যা একসময় আন্তর্জাতিক সমর্থন পেত, আজ তা প্রায় অবাস্তব মনে হচ্ছে। পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ, জেরুজালেমের অবস্থান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এই পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে বলেও মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।
অবকাঠামোর ধ্বংস ও বাস্তুচ্যুতি: ইসরায়েলের অবিরাম বোমা হামলায় গাজার অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলে প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা অস্থায়ী শিবিরে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করছে, যেখানে মৌলিক সেবা ও নিরাপত্তার অভাব প্রকট।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘের ভূমিকা: গাজার মানবিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা অনেকের মতে একপেশে মনোভাবের প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ গাজায় স্বাস্থ্যকর্মীদের হত্যার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
পরিশেষে, একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বৈত নীতি পরিহার করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি দেবে এবং ইসরায়েলকেও আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করবে। তার আগে গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে শুধু মানুষই নয়, সমাহিত হয়ে যাচ্ছে মানবতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ববিবেক! উত্তরণের উপায় খুঁজতে দেরি হলে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে সহিংসতা। এতে করে মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অ্যাডভোকেট, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ফেনী
মধুরঃধৎবশধুরু.২৪Ñমসধরষ.পড়স
ভারতে মুসলিমদের জমি দখল: পারস্পরিক সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেবে?
হেনা শিকদার
ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং বহু স্তরের। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি, ভাষা ও অর্থনীতির দিক থেকে দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বহুস্তরীয় ও জটিল। এই দুটি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে উভয় দেশেই সংখ্যালঘু অধিকার একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভারতে মুসলিমদের জমি দখলের অভিযোগ-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনা এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভিযোগগুলো বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও মাঝে মাঝে উত্তেজনার ইতিহাস থাকায় যে কোনো একটি দেশে বৃহৎ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উদ্বেগের বিষয় অন্য দেশেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ এ ধরনের বিষয়গুলোর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতের মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ২৫০টি বাড়িঘর, দোকান ও একটি শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে ২ দশমিক ১ হেক্টর (৫ দশমিক ২৭ একর) বিস্তৃত জমি খালি করা হয়, যা মধ্যপ্রদেশ ওয়াক্ফ বোর্ডের মালিকানাধীন ছিল। এই ফবসড়ষরঃরড়হং শহরের বিখ্যাত মহাকালেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে এক বিলিয়ন ডলারের একটি সরকারি প্রকল্পের অংশ হিসেবে চালানো হয়েছিল। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের জুনে উজ্জয়িনীর এক রাজস্ব কর্মকর্তা এই ওয়াক্ফ জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৫ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, এটি ওয়াক্ফ জমি এবং রাজ্য ওয়াক্ফ বোর্ডের কাছ থেকে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ নেয়া উচিত। তবে এক মাস পর উজ্জয়িনী জেলা প্রশাসন আদেশ জারি করে জানায়, ‘সামাজিক কারণে’ জমি অধিগ্রহণে অনুমতির প্রয়োজন নেই। এই অধিগ্রহণকে ওয়াক্ফ আইনের সরাসরি লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন আইনজীবী সোহেল খান, যিনি এই ঘটনাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন। যদিও সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩৩০ মিলিয়ন রুপি (৩.৮ মিলিয়ন ডলার) দিয়েছে, তবে শহরের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ওয়াক্ফ বোর্ড এই অর্থ দাবি করেনি। মধ্যপ্রদেশ ওয়াক্ফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি উজ্জয়িনীর একজন বিজেপি নেতা, তিনি বলেছেন দলের আদেশ মেনে চলবেন।
ভারতে ২০ কোটিরও বেশি মুসলিমের আবাসস্থলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ওয়াক্ফ সম্পদ ৮ লাখ ৭২ হাজার হেক্টরেরও বেশি রয়েছে, যা প্রায় ৪ লাখ ৫ হাজার হেক্টর (১০ লাখ একর) জুড়ে বিস্তৃত, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ‘ওয়াক্ফ’ হলো মুসলমানদের ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে দান করা সম্পত্তি, যা বিক্রি বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। প্রতিটি রাজ্য ও ফেডারেল অঞ্চলে ওয়াক্ফ বোর্ড এসব সম্পত্তি পরিচালনা করে, যা দেশটির অন্যতম বৃহৎ ভূ-সম্পত্তির মালিক। বছরের পর বছর ধরে প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে ওয়াক্ফ জমির প্লট বিক্রি করেছে। জমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের সময় মাঝে মাঝে ওয়াক্ফ জমি সরকারি সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ড হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু-বিষয়ক মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫৪ হাজার ৯২৯টি ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। উজ্জয়িনীর ঘটনা স্থানীয় উন্নয়নের অজুহাতে ঘটানো হলেও ভারতে মুসলিমদের মালিকানাধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ওপর কথিত দখলের বৃহত্তর চিত্রের অংশ। এই সম্পত্তিগুলোর বিশাল পরিমাণ ও মূল্য বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাছে লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে।
ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল ২০২৪: আইনি পরিবর্তন এবং বিতর্কিত বিষয়: ‘ওয়াক্ফ (সংশোধনী) ২০২৪’ বিলটি ২০২৫ সালের এপ্রিলে ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) পাস হয়েছে। বিলটি ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও ভোটাভুটি হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই সংশোধনীগুলোর উদ্দেশ্য হলো ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা মোকাবিলা করা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা। সরকার আরও দাবি করেছে, এই সম্পত্তি থেকে অর্জিত রাজস্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ করে দরিদ্র ও মহিলাদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে এবং এটি একটি ‘মুসলিম-বান্ধব সংস্কার’।
সংশোধিত বিলের মূল বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে: ওয়াক্ফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা; দীর্ঘদিনের ব্যবহারের (ওয়াক্ফ বাই ইউজার) ভিত্তিতে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য করার প্রথার বিলোপ, তবে বিতর্কিত নয় ও সরকারি মালিকানাধীন নয়, এমন সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে। বিতর্কিত সম্পত্তির বিষয়ে জেলা কালেক্টর সিদ্ধান্ত নেবেন; ওয়াক্ফ হিসেবে চিহ্নিত যেকোনো সরকারি সম্পত্তি সেই মর্যাদা হারাবে; ওয়াক্ফ বোর্ডগুলোর অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন এবং নিরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম তৈরির ক্ষমতা, যারা পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করছেন, কেবল তারাই ওয়াক্ফ দান করতে পারবেন এবং ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করার অধিকারের প্রবর্তন। এ ছাড়া বিলটিতে নারী এবং শিয়া, পশমান্দা ও বোহরা সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য ওয়াক্ফ বোর্ডে আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে।
তবে বিরোধী দল এবং মুসলিম সংগঠনগুলো এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তারা এটিকে ‘মুসলিম-বিরোধী’, ‘অসাংবিধানিক’ ও মুসলিমদের জমি দখলের জন্য বিজেপির একটি কৌশল বলে অভিহিত করেছে। তাদের আশঙ্কা, ‘ওয়াক্ফ বাই ইউজার’-এর বিলোপ এবং সরকারি সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিধানের মাধ্যমে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত না হওয়া সম্পত্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। বিরোধী দলগুলি সম্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ওয়াক্ফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা হয়েছে, কারণ এটিকে বৈষম্যমূলক ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মুসলিম সংগঠনগুলির বিশ্বাস, এই সংশোধনের আসল উদ্দেশ্য হলো বিজেপি সমর্থকদের কমিটি ও বোর্ডগুলিয় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করা। ‘ইসলাম পালনকারী মুসলিম’-এর সংজ্ঞা এবং এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে বিজেপি তার হিন্দুত্ববাদী ভোটব্যাংককে তুষ্ট করার জন্য এই বিলটি এনেছে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এই বিলটিকে বৈষম্যমূলক এবং মুসলিম নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। কংগ্রেস পার্টি ঘোষণা করেছে, তারা সুপ্রিম কোর্টে এই বিলের সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। সরকারের ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির দাবির বিপরীতে ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল গভীরভাবে বিতর্কিত। বিরোধী দল ও মুসলিম সংগঠনগুলো এটিকে তাদের সম্পত্তির অধিকার ও ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরাসরি আক্রমণ হিসেবে দেখছে, যা বিদ্যমান উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া ও জনগণের মতামত: বাংলাদেশ সরকার বা তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে মুসলিমদের জমি দখল বা ‘ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল ২০২৪’ নিয়ে সরাসরি কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশি গণমাধ্যম এ বিষয়ে বেশ সোচ্চার। প্রায়ই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের (যেমন, আল জাজিরা) প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদগুলোয় বিলটিকে মুসলিমদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার অধিকার প্রদানকারী এবং ঐতিহাসিক মসজিদ ও দরগাহগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশি মিডিয়ায় এই বিলের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
অন্যদিকে বাংলাদেশি গণমাধ্যমে ভারতের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর কথিত নির্যাতন এবং ভারতের গণমাধ্যমের সে-সংক্রান্ত ভুল তথ্য প্রচারের বিষয়টিও উঠে এসেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু ইস্যু এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। অতীতে দেখা গেছে, ভারতে মুসলিমদের কোনো ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব বাংলাদেশেও অনুভূত হয় এবং জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল ও মুসলিমদের জমি দখলের অভিযোগের বিষয়টি বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সহানুভূতি ও উদ্বেগের জš§ দিতে পারে। এর ফলে ভারতে মুসলিমদের প্রতি অবিচারের ধারণা আরও বদ্ধমূল হতে পারে, যা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতীতে ভারতবিরোধী মনোভাবের কিছু দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে দেখা গেছে এবং এই ঘটনা সেই মনোভাবকে আরও ইন্ধন জোগাতে পারে।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: সংখ্যালঘু ইস্যু ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব: অতীতে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিভিন্ন ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলার ঘটনাও ঘটেছিল। এই ঘটনা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী সংবেদনশীলতা তৈরি করে। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গাও ভারতে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, যদিও এর সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর কতটা পড়েছিল, তা প্রদত্ত তথ্যে স্পষ্ট নয়।
অন্যদিকে ভারতও বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতনের বিষয় নিয়ে প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ও সম্পত্তির ওপর হামলার ঘটনা এবং একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তার নিয়ে ভারত সরকারের উদ্বেগের কথা জানা গেছে। তবে বাংলাদেশ সরকার এই অভিযোগগুলিকে অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং ভারতীয় গণমাধ্যমকে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করেছে। ঐতিহাসিক ভূমি সীমানা নিয়েও দুই দেশের মধ্যে কিছু সমস্যা ছিল।
কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা: কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক আলোচনাগুলো মূলত বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃতি এবং বৃহত্তর দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে উভয় দেশ একে অপরের কূটনীতিকদের ডেকে পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে একটি বৈঠকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে মুসলিমদের জমি দখলের বিষয়টি ভবিষ্যতে কূটনৈতিক আলোচনায় উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ পেলে।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের মতামত: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের মতে, ভারতে মুসলিমদের জমি দখল এবং ওয়াক্ফ সংশোধনী বিলের মতো বিষয়গুলো বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের আশঙ্কা, ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারের আচরণ আঞ্চলিক নেতৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ সরকারের হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ভারতের উদ্বেগের বিপরীতে ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতের দ্বিমুখী নীতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জটিল ও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব বাড়ছে এবং এর অন্যতম কারণ ভারতে মুসলিমদের প্রতি আচরণের উদ্বেগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের উচিত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখানো এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে। তবে দিল্লিকে অবশ্যই বাংলাদেশে ‘ভারতবিরোধী’ মনোভাব মোকাবিলায় আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবং পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল মুসলিমদের প্রান্তিক করার এবং তাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেয়ার একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা সম্পর্ককে আরও খারাপ করবে। এই বিলের মাধ্যমে ঐতিহাসিক মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আশঙ্কাও রয়েছে।
ভারতে মুসলিমদের জমি দখলের অভিযোগ এবং ‘ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল ২০২৪’ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর একটি সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সাম্প্রতিককালে মুসলিমদের সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা এবং সরকারের ওয়াক্ফ সম্পত্তির ওপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনি পরিবর্তন আনার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াক্ফ বিলের উদ্দেশ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা বলা হলেও বহু মুসলিম সংগঠন ও বিরোধী দল এটিকে মুসলিমদের জমি দখলের একটি কৌশল এবং সংখ্যালঘু অধিকারের ওপর আক্রমণ হিসেবে দেখছে।
বাংলাদেশে এই ঘটনাগুলো উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং গণমাধ্যমে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ‘ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল ২০২৪’ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও জনমনে এর প্রভাব পড়তে পারে এবং ভারতবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে পারে।
উভয় দেশের উচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং যেকোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ রোধে পদক্ষেপ নেয়া। নিয়মিত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর সমাধান খোঁজা উচিত, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয় পক্ষকেই সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবাসী আয়ে ফিরল দেশের প্রতি আস্থা
দেশে গত মার্চে রেমিট্যান্স এসেছে ৩২৯ কোটি মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগেও অর্থনীতির সূচকগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আমরা গভীর উদ্বেগে ছিলাম। তখন রিজার্ভ কমে যাচ্ছিল, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, আর প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ছিল আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী। ৩২৯ সংখ্যাটি নিছক একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি একটি বার্তা, দেশের বাইরে থাকা প্রবাসীরা আবারও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, বৈধপথে পাঠানো টাকাও ঠিকঠাক পৌঁছায় এবং দেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে নিরাপদ হাতে আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৭৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের (২০২৩-২৪) একই সময়কালের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। শুধু ফেব্রুয়ারিতেই এসেছে ২২০ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১০ কোটি ডলার এবং ডিসেম্বরেও একই ধারায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ২০০ কোটির ঘরে। এই আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনের মূল কথাটি হলো, সরকার বদলেছে, শাসনের ধরন বদলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, আস্থার জায়গা বদলেছে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে মুক্ত, প্রশাসনিকভাবে উদার এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দৃঢ়। যে প্রশাসন জনতার কথায় কান দেয়, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং জাতীয় স্বার্থে কাজ করে, তাতে মানুষ বিশ্বাস রাখবেই।
সরকার প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহ দিতে ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা চালু রেখেছে। মোবাইল অ্যাপভিত্তিক রেমিট্যান্স সিস্টেমে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, হুন্ডি বন্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা এবং প্রবাসী কূটনৈতিক মিশনগুলোর দায়িত্বশীলতা, এসব মিলেই তৈরি হয়েছে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। প্রবাসীরা এখন জানেন, তারা যে ডলার পাঠাচ্ছেন, তা দেশের কাজে লাগছে, মাঝপথে হারিয়ে যাচ্ছে না।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, শুধু রেমিট্যান্স প্রবাহ নয়, এই প্রবণতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যও আশাব্যঞ্জক। রিজার্ভ ঘাটতি কমেছে, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়েছে এবং বৈদেশিক লেনদেনের চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এর অর্থ, প্রবাসী আয়ের এই ধারা অর্থনীতির রক্তপ্রবাহের মতো কাজ করছে। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। এই আস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে বৈধ শ্রমবাজার আরও প্রসারিত করতে হবে, প্রবাসী কল্যাণব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং রেমিট্যান্সের ব্যবহারকে উৎপাদনমুখী খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তা না হলে এই অর্থ কেবল ভোগব্যয়ের পেছনে ব্যয় হয়ে যাবে, দেশের কাঠামোগত উন্নয়নে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলবে না।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রবাসীদের এই আস্থা যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে শুধু রেমিট্যান্স নয়, দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক সূচকেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে। এই আস্থা আর স্থিতিশীলতার যুগ যেন দীর্ঘায়িত হয়, সেটাই এখন প্রত্যাশা।
চোখের শুষ্কতা কেন বাড়ছে
আজকাল ড্রাই আই বা চোখের শুষ্কতার সমস্যা বাড়ছে। বিশেষ করে যারা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন বা দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখেন বা মুঠোফোন ব্যবহার করেন, এমন ব্যক্তিদের অনেকেই ড্রাই আইয়ের সমস্যায় পড়েন। এসি বা ফ্যানের সরাসরি বাতাস, ঘরে কম আর্দ্রতা ও বায়ুদূষণের কারণেও ড্রাই আই হতে পারে। ডায়াবেটিস, সিজোগ্রেন সিনড্রোম ও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসের মতো পরিস্থিতিও চোখের শুষ্কতার জন্য দায়ী। কিছু ওষুধ যেমন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি চোখের শুষ্কতা ঘটাতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও মেনোপজের পর নারীদের চোখ শুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখের প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি। এই পানি শুকিয়ে যাওয়া অনেক রোগের লক্ষণ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ পানির উৎপাদন কিছুটা কমে। ৫০ বছর বয়সের পর পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়।
কীভাবে বুঝবেন: চোখে কাঁটার মতো লাগা, কিছু বিঁধে থাকার মতো অনুভূতি ও চোখ দিয়ে পানি পড়া চোখের শুষ্কতার পূর্বলক্ষণ। এ কারণে মাথাব্যথা থেকে জ্বর ও নাক বন্ধ থাকার রোগও হয়ে থাকে। বারবার মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখে পর্যাপ্ত লালাগ্রন্থি না থাকা বা কথা জড়িয়ে যাওয়ার সমস্যাও থাকতে পারে।
চিকিৎসা কী: চিকিৎসক শুরুতেই চোখের পানির গুণগত মান, পরিমাণ ও গঠনসম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা করবেন। ভিটামিন ‘এ’-এর ব্যবহার এবং কারণ অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করলে চোখের শুষ্কতা দূর করা যায়। সব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম চোখের পানি ব্যবহার করা যায়। মিথাইল সেলুলোজ, সফট কন্ট্যাক্ট লেন্স ও প্যারোটিভ ডাক্ট প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেও চোখের শুষ্কতার প্রতিকার করা যায়।
ঘরোয়া প্রতিকার কী: প্রচুর পানি পান করতে হবে। নিয়মিত চোখের ব্যায়াম করা যায়। খাদ্যতালিকায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার রাখুন। একনাগাড়ে না তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলা ভালো। মিনিটে ১৫-৩০ বার চোখের পাতা পিটপিট করা প্রয়োজন। ২০ সেকেন্ডের বেশি চোখ খোলা রাখা উচিত নয়। ২০ মিনিট পরপর মনিটর থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ সরাতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার সময় চোখে আই প্রোটেক্টর স্পেকটিক্যাল ব্যবহার করা ভালো। বাইরে বেরোলে ভালো মানের রোদচশমা পরার অভ্যাস করুন। হালকা গরম পানিতে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ডুবিয়ে সেই কাপড় নিংড়ে নিয়ে চোখের ওপর পাঁচ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা চাপে চোখের ওপরের ও নিচের পাতায় কাপড়টা মালিশ করলে চোখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতে চোখের আর্দ্রতাও বাড়বে। পরিষ্কার তুলায় নারকেল তেল দিয়ে চোখের ওপর ১৫ মিনিট রাখতে পারেন। দিনে বেশ কয়েকবার এটা করা যায়। পরিষ্কার টিস্যুতে অ্যালোভেরা জেল নিয়ে চোখের নিচের পাতায় আলতো হাতে মালিশ করুন। ১০ মিনিট পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন। এটা দিনে দুবার করতে পারেন।
অধ্যাপক ডা. সৈয়দ এ কে আজাদ
চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ফ্যাকো সার্জন বিভাগীয় প্রধান
আল-রাজী হাসপাতাল, ফার্মগেট, ঢাকা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস আজ। ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে তার জš§। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা, পরে হুগলির ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের যে দুজন ছাত্র বিএ পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাদের একজন। তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিম্ন নির্বাহী চাকরিতে (সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস) যোগ দেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করেন। তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাকে ১৮৯১ সালে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি প্রদান করে।
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসেবে মফস্বলে চাকরিরত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলার জনগণের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংসর্গ এবং তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া থেকে তিনি তার উপন্যাসের চরিত্র গ্রহণ করেন।
চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা রচনা করেন। ১৮৮৭ সালের মধ্যে তার অন্যান্য গদ্য রচনাসহ মোট ১৪টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ থেকে বঙ্কিমমনীষা রাজনীতি ও ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেসময় তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। আনন্দমঠ (১৮৮২) সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। বাংলা উপন্যাস ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাময়িকী সাহিত্যের প্রসারেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তার বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন: রাজসিংহ (১৮৮২) এবং সীতারাম (১৮৮৮)। কোনো কোনোটিতে আবার ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধেও হিন্দুজাতির বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন: দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ।
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মধ্যপন্থি রাজনৈতিক নেতারা প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী সেøাগানে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু স্বদেশী যুগের যুবসমাজের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা এবং তার মতাদর্শে যুবসমাজের মধ্যে যে উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল, তা কংগ্রেসকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে এবং একটি জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হতে প্রভাবিত করে। এরপর কংগ্রেস তার জাতীয় রাজনীতির সেøাগান হিসেবে ‘বন্দে মাতরম্’কে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তা ব্যবহƒত হতে থাকে। অতীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্যব্যক্তিত্ব হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের আবির্ভাব পর্যন্ত সবার কাছে, এমনকি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কাছেও সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন। ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [সংগৃহীত]
গাজা: ক্রমবর্ধমান মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট
গাজী তারেক আজিজ: গাজা উপত্যকা ফিলিস্তিনের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, যা দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি দখলদারত্ব, অবরোধ ও সংঘাতের শিকার। ইসরায়েল ও মিসরের অবরোধের ফলে গাজার অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সাধারণ জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত এক দশকে গাজা উপত্যকা হয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম আলোচনার কেন্দ্র, যা ইসরায়েলি বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়ে মানবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। ইসরায়েল-হামাস সংঘাত নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও শক্তির রাজনীতিকে। গাজার বর্তমান অবস্থা কেবল একটি ভূখণ্ডের সংকট নয়, বরং এটি আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক মূল্যবোধের একটি প্রতিচ্ছবি।
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, নাকি নতুন অধ্যায়: গাজার সংকট নতুন নয়। ২০০৭ সালে হামাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর থেকে এই ভূখণ্ড কার্যত এক বৃহৎ খোলা কারাগারে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েল ও মিসরের অবরোধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়েন, ও দারিদ্র্যের মধ্যে বন্দি প্রায় ২৩ লাখ মানুষ প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়। বলা বা ব্যাখ্যা করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে যায় সুস্থ স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষের।
তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সহিংসতা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ। হামাসের হামলায় ইসরায়েলের বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল পাল্টা আক্রমণ শুরু করে গাজায়। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ নিহত, লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত এবং অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে এমন জনমানবহীন ধ্বংসযজ্ঞ কল্পনাও করা কঠিন, যা চলছে বিরামহীনভাবে!
সাম্প্রতিক সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়: ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। এই সংঘাতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা যায়, যার মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। এ ছাড়া ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬২ জন আহত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ১৫ প্যালেস্টিনীয় স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন হামলার ভিডিও ধারণ করেছিলেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। যদিও ইসরায়েল এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও দ্বৈত মানদণ্ড: গাজার বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় যে দ্বৈত মানদণ্ড রয়েছে, তা আজ আর অজানা নয়। পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ শুরুতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেও গাজার বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার তীব্রতা বাড়ে। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যদের ভূমিকায় দেখা গেছে কৌশলগত দ্বিধাÑএকদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা, যা কেবলই মোড়লি রাষ্ট্রের অবিমৃষ্যকারী বৈ আর কিছু কি? এই দ্বৈত মানদণ্ড বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছেÑইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতায় যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ, গাজার ক্ষেত্রে সেই নৈতিক জোর কোথায় হারিয়ে যায়? কেনই বা বিশ্ববিবেক এতটা নীরব থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে, তাও কি ভাববার বিষয় নয়? নাকি এভাবেই ধ্বংস করে দেয়া হবে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও নাগরিকদের? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, আরব বিশ্বও কেন মৌনব্রত পালন করছে?
আরব বিশ্বের মৌনতা ও বাস্তবতা: আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও জনমনে প্রবল ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখা গেছে, অনেক সরকার কৌশলগতভাবে নীরব থেকেছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে হাঁটছিল এবং গাজার যুদ্ধ সেই প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুললেও পুরোপুরি থামায়নি। আদতে থামানোর কোনো উদ্যোগও লক্ষণীয় ছিল বলেও মনে হচ্ছে না! উপরন্তু তারা যেন ‘মামা শ্বশুরের সামনে ভাগনে বউয়ের ভূমিকায়’ থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরে জানাবে ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে!
মিসরের ভূমিকাও সমালোচিত। রাফা সীমান্ত অল্প সময়ের জন্য খুললেও অধিকাংশ সময়ই তা বন্ধ ছিল। মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা, আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থান না দেওয়াÑসবই প্রমাণ করে, গাজা শুধু ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট নয়, এটি আরব বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। এতে বোঝা যায়, মানবিক সংকটের ঊর্ধ্বে একেক দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থই যার যার কাছে বড়, যা তাদের আচরণে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
হামাসÑপ্রতিরোধ না সন্ত্রাস: হামাসের ভূমিকাও এ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেদের ‘প্রতিরোধ আন্দোলন’ হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ করে হামলা চালানোর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের সন্ত্রাসী তকমা অটুট রয়েছে। এর ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নটিও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলকে একটি ‘নিরাপত্তা হুমকি’ উপস্থাপন করতে সহায়তা করে, যার ওপর ভিত্তি করে ইসরায়েল তার আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে আমেরিকা ও মিত্র শক্তির।
তবে হামাসের উত্থানের মূল কারণগুলো হলোÑইসরায়েলি দখলদারত্ব, রাজনৈতিক দমন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। সেগুলো বিশ্লেষণে না এনে শুধু প্রতিক্রিয়াকে দোষারোপ করাই কি যথাযথ? কার্যত যা-ই হোক একেবারে সেসবও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তারপরও ভুক্তভোগী গাজা তথা ফিলিস্তিনের বেসামরিক জনগণ।
মিডিয়া ও তথ্য যুদ্ধ: গাজার যুদ্ধ আরেকটি বড় মাত্রা পেয়েছে তথ্যমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পশ্চিমা মূলধারার সংবাদমাধ্যমে অনেক সময়ই পক্ষপাতদুষ্টতা চোখে পড়ে, যেখানে ইসরায়েলের প্রাণহানিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর গাজার গণহত্যা তুলনামূলকভাবে গৌণ করে উপস্থাপন করা হয়। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের জোয়ার দেখা গেছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজšে§র মধ্যে। যে কোনো ঘটনাই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। এতে করে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যেভাবেই প্রচার করুক না কেন, সুরের যেমন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না, তেমনই কান্নার বা চোখের জলেরও আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না, যা দেখেই মানুষ বুঝে নিতে পারে। কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয় না।
এটি প্রমাণ করে, তথ্য এখন আর একমুখী নয়। মানুষ নিজেরাই ছবি, ভিডিও ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরছে। যদিও ইসরায়েল বারবার গাজায় ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তথ্যপ্রবাহ থামানোর চেষ্টা করেছে, তা পুরোপুরি সফল হয়নি, যা ইসরায়েলের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক উš§ত্ততা প্রকাশে বিঘ্ন না ঘটিয়ে আরও সহায়ক হয়। এতে বিশ্ববাসীর নজর এড়িয়ে যায়নি।
সামনে কী: গাজার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে বিশ্ব। যদি যুদ্ধ থেমেও যায়, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এটি কেবল অস্থায়ী বিরতি হবে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান, যা একসময় আন্তর্জাতিক সমর্থন পেত, আজ তা প্রায় অবাস্তব মনে হচ্ছে। পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ, জেরুজালেমের অবস্থান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এই পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে বলেও মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।
অবকাঠামোর ধ্বংস ও বাস্তুচ্যুতি: ইসরায়েলের অবিরাম বোমা হামলায় গাজার অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলে প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা অস্থায়ী শিবিরে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করছে, যেখানে মৌলিক সেবা ও নিরাপত্তার অভাব প্রকট।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘের ভূমিকা: গাজার মানবিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। জাতিসংঘ একাধিকবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা কার্যকর হয়নি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা অনেকের মতে একপেশে মনোভাবের প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ গাজায় স্বাস্থ্যকর্মীদের হত্যার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
পরিশেষে, একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বৈত নীতি পরিহার করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি দেবে এবং ইসরায়েলকেও আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করবে। তার আগে গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে শুধু মানুষই নয়, সমাহিত হয়ে যাচ্ছে মানবতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ববিবেক! উত্তরণের উপায় খুঁজতে দেরি হলে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে সহিংসতা। এতে করে মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অ্যাডভোকেট, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ফেনী