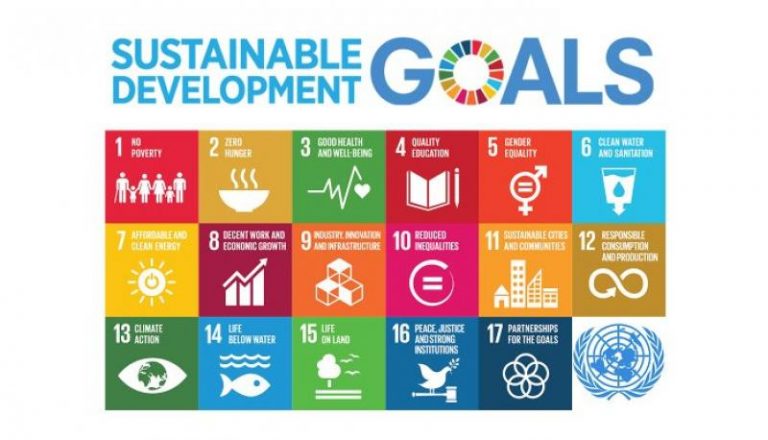মাসুম বিল্লাহ: যে কোনো দেশের অগ্রগতির জন্য বর্তমানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বের সব দেশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক অগ্রসর। আর এসব খাতে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত গবেষণা। কিন্তু সেই গবেষণা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নেই। ফলে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে আগামী দিনে শক্তিশালী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে।
এমন পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) অগ্রগতি প্রতিবেদনে। সম্প্রতি ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। এটি দ্বিতীয় অগ্রগতি প্রতিবেদন। এর আগে ২০১৮ সালে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।
অগ্রগতি প্রতিবেদনের তথ্যমতে, এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য বৈশ্বিক প্রযুক্তি সহজীকরণ কৌশল ও একটি প্রযুক্তি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গবেষণা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ কম। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (এসটিআই) অন্যান্য খাতেও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।
মূলত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সক্ষমতা একটি দেশের যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভ‚মিকা রাখে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় বাংলাদেশ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছে। এসডিজি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের জ্বালানি উৎপাদন ও তা ব্যবহারে পরিবেশগত নিরাপদ প্রযুক্তিতে অধিগম্যতা থাকা দরকার বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
জানা যায়, বাংলাদেশ সব এসটিআই সূচকে পিছিয়ে। মাথাপিছু গবেষণা উন্নয়ন ব্যয়, প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে গবেষণায় মানবসম্পদ, প্রযুক্তি, গ্রহণ ও প্রদান এবং মেধাস্বত্ব (পেটেন্ট) নিবন্ধন প্রভৃতি বিষয় এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ের প্রতিটিতে প্রতিদ্ব›দ্বী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য এসটিআই নীতিমালা পুনরায় পর্যালোচনা করা ও তা শক্তিশালী করার ওপর অগ্রগতি প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (জ্যেষ্ঠ সচিব) ড. শামসুল আলম শেয়ার বিজকে বলেন, এসডিজি অর্জন করতে হলে সামনের বছরগুলোয় কোন কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে, সে বিষয়টিই অগ্রগতি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ২০২০ সালের জন্য ধার্যকৃত মাইলফলক এরই মধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেদনে সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। তবে করোনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এসডিজি অর্জন প্রক্রিয়া কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হতে হবে।
টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও চর্চা তৈরি এবং তা অবলম্বন করতে হলে এসটিআই সূচকে অগ্রগতি অর্জনের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা রাখতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, একটি সহযোগিতাপরায়ণ আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের জন্য উপকারী হতে পারে নানা খাতে; যেমন কৃষি ও খাদ্যসংক্রান্ত গবেষণা-উন্নয়ন এবং সেরা কৃষি অনুশীলন (জিএপি) বিনিময়ে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা ও জমির ব্যবহার উন্নয়নে কৃষিজ বৈচিত্র্য ও জার্মপ্লাজম নিয়ে।
আঞ্চলিক সহযোগিতা বিচিত্র খাতে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করবে। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন কিংবা গবাদিপশু পালন থেকে রোগবালাই দমনসহ নানা বিষয়ে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়। একই সময়ে রূপান্তরশীল উন্নয়নের নীতিমালায় দক্ষতা সৃষ্টি এবং গবেষণা-উন্নয়নে বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটি দরকার কাঠামোগত রূপান্তরের বিকাশের জন্য বিশেষ করে আরও কার্যকর ও কম সম্পদের ওপর নির্ভরশীল শিল্প প্রসারের জন্য।
তবে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় কিছু উদ্ভাবনের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু উদ্ভাবনের এ গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে না, আগামী দিনে টিকে থাকার জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
বাংলাদেশের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সাশ্রয়ী পণ্য ও সুলভ প্রসেস সৃষ্টিতে দারুণ সম্ভাবনা দেখিয়েছে। মিতব্যয়ী প্রকৌশল সক্ষমতার মাধ্যমে বাংলাদেশ জীবনরক্ষাকারী স্বল্পমূল্যের খাবার স্যালাইন ও পানি পরিশোধন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।
এই সক্ষমতা কাজে আসতে পারে কম কার্বন (সিওটু) নিঃসরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদে কম চাপ প্রয়োগ করার উপায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। এটি বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আরও কম মূল্যের পণ্য ও সেবা তৈরির দিকে এগিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের মিতব্যয়ী উদ্ভাবন প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউটিলিটি মডেল অথবা ‘পেটি পেটেন্ট’ অবলম্বন করতে পারে। এটি চলমান উদ্ভাবনের জন্য কিছু সময় সুরক্ষা দিতে পারে। এছাড়া ট্রিপস চুক্তির আওতায় যেসব নমনীয়তা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে দেশীয় উদ্ভাবন প্রসার করা যেতে পারে।