মনজুরুল আলম মুকুল : ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান, স্বাধীনতা অর্জন, সামাজিক অত্যাচার ও অসমতা দূরীকরণ এবং জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চত করার জন্য। সারা বিশ্বের জনগণের অধিকারের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে ফরাসি বিপ্লব।
আমরা বইপুস্তকে জেনেছি ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ দখলের মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং ১৭৯৯ সালে শেষ হয়। স্থায়ী ছিল ১০ বছর। তবে ফ্রান্সে একটি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের ও সুস্থ ধারার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেতে প্রায় ১০০ বছর সময় লেগে ছিল।
ইতিহাসে দেখা যায়, এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ছিল বটে, তবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও আগের শাসন ব্যবস্থা বার বার ফিরে এসেছিল। দেশের অভ্যন্তরে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, ব্যক্তিস্বার্থের নীতি বিদ্যমান ছিল, তেমনি ইউরোপের অন্যান্য রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা দেশগুলো থেকে নানা ধরনের বিরোধিতা ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। বহুবার সংবিধান রচিত হয়েছে, বহুবার স্থগিতও হয়েছে আবার পরিবর্তন হয়েছে। এই জন্য ফরাসিদের বার বার রক্ত দিয়ে হয়েছে।
বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে ফরাসি জনগণ রাজা ষোড়শ লুই ও তার রাজপরিবারের অত্যাচারে চরম ক্ষুব্ধ ছিল। তৎকালীন ফ্রান্সের সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথমে ছিল ধর্মীয় নেতা বা যাজক শ্রেণি যারা মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ। দ্বিতীয় অংশে ছিল এলিট বা অভিজাত শ্রেণি বা রাজপরিবারের আশপাশের লোকজন, যারা ছিল মোট জনসংখ্যার ১ দশমিক ৫ শতাংশ তবে মোট জমির ৩ ভাগের ১ ভাগের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তৃতীয় অংশে ছিল সাধারণ জনগণ যার মধ্যে ছিল কৃষক, শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ী যারা ছিল মোট জন সংখ্যার ৯৭ শতাংশ।
তৃতীয় অংশের মানুষেরা ছিল অত্যন্ত শোষিত, তাদের ওপর চাপানো হতো শুধু কর আর কর, যে কারণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাদের কোনো উন্নয়ন ছিল না, কোনো ভোটের অধিকার ছিল না। তাদের করের টাকায় রাজপরিবার ও ওপরের শ্রেণির লোকেরা ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল।
কোনো আইন হতে হলে তৎকালীন স্টেট জেনারেলে পাস হওয়া লাগত। স্টেট জেনারেলে সদস্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২১৪ জন। যার মধ্যে যাজক শ্রেণির ৩০০ জন, অভিজাত শ্রেণির ৩০০ জন ও সাধারণ মানুষের ৬১৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। সবচেয়ে মজার বিষয় ভোট মাথাপিছু ছিল না, তিন সম্প্রদায়ের জন্য ভোট ছিল মাত্র তিনটি। স্টেট জেনারেলে সাধারণ নাগরিকের অনুকূলে কোনো আইন পাস হতো না কেননা যাজক ও অভিজাত শ্রেণির দুই ভোট সবসময় একই দিকে পড়ত।
যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজকীয় ব্যয়ের জন্য ফ্রান্সে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা ষোড়শ লুই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও রুটির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ অনেকে খাবারের জন্য গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে।
এই সময় রাজা ষোড়শ লুই যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপর কর আরোপের সিদ্ধান্ত নিলে তাদের একটা অংশ রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং জনগণকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ দখলের মাধ্যমে এই ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ১৭৯১ নতুন সংবিধান রচনা করতে বাধ্য করা হয়।
এমন সময় ইউরোপের অন্যান্য রাজতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রগুলো ষোড়শ লুইকে বিভিন্ন ভাবে সমর্থন জানাতে থাকলে জনগণ আরও ক্ষেপে যায়। এক পর্যায় ২১ জানুয়ারি ১৭৯৩ সালে ষোড়শ লুইকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার মৃত্যু এক হাজার বছরেরও বেশি ধারাবাহিক ফরাসি রাজতন্ত্রের সমাপ্তি নিয়ে আসে এমন অনেকে মনে করে।
একদিকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিশৃঙ্খলা অন্যদিকে ইউরোপের অন্য রাজশক্তির শত্রুতা ফ্রান্সকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। এমন অবস্থার মধ্যে আবির্ভাব ঘটে থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের যিনি ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সময়কার একজন জেনারেল।
ষোড়শ লুইকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড পরবর্তী সময়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইতালি, লোম্বার্ডি, পাপাল অস্ট্রিয়া, রাইনল্যান্ড ভেনিসসহ ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আনেন। জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি জনপ্রিয় হন। এক সময় একনায়ক ও স্বৈরচারী শাসক হয়ে ওঠেন। নেপোলিয়ন ওয়ান নামে ফ্রান্সের সম্রাটও হন।
তবে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানটি মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয় এবং তিনি পরাজিত হন। এক সময় ষষ্ঠ কোয়ালিশন ফ্রান্সে আগ্রাসন চালায়। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুতে পরাজিত হওয়ার পর নেপোলিয়নকে ব্রিটিশরা আটলান্টিক মহাসাগরের প্রত্যন্ত দ্বীপ সেন্ট হেলেনাতে নির্বাসনে পাঠায়। এরপর ইউরোপের রাজশক্তিগুলো মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র চালু হবে। ২৩ বছর পর রাজা লুই ষোড়শের ভাই লুই অষ্টাদশ আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন এবং তিনি ১৮২৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। তবে তিনি জনগণের কথা বিবেচনা করে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা করেন।
অষ্টাদশ লুইয়ের কোনো সন্তান ছিল না এবং তার মৃত্যুর পর রাজা হন তার ভাই চার্লস দশম। তবে চার্লস দশম লুই অষ্টাদশের মতো উদার ছিলেন না। তিনি রাজতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করলে আবার গোলযোগ দেখা যায়। এমন অবস্থায় লুই ফিলিপ প্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তার রাজত্বকাল ছিল ১৮৩০-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত। ১৮৪৭ সালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সূত্রপাতের পর তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। লুই-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যিনি নেপোলিয়ন তৃতীয় নামে পরিচিত, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম নেপোলিয়নের ভাই লুই বোনাপার্টের পুত্র। তবে তিনি কূটচালের মাধ্যমে ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচন বাধা দিয়ে রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ঘটান। ১৮৫২ সালে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এই নেপোলিয়ন তৃতীয়কে ১৮৭০ ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
এরপর ১৮৭১ সালের নির্বাচন ও ১৮৭৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রান্সে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল সংসদ প্রতিষ্ঠা হয়।
বিপ্লব নিয়ে আমাদের ভেতরে এক ধরনের হীনমন্যতা কাজ করে। যেমন- ছাত্র-জনতার ২৪ সালের জুলাই বিপ্লবকে সমর্থন করলে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা হয় কিনা এমনটা অনেকে ভেবে থাকে। আবার অনেকে মনে করে শুধু ১৯৭১ সালকে ধরতে হবে। তারা ১৯৪৭ সাল ও ব্রিটিশবিরোধী অন্যান্য আন্দোলনকে সামনে নিয়ে আসতে চায় না।
১৭৫৭ সালের পথ ধরে ১৯৪৭ এরপর ১৯৭১ এরপর ২০২৪। কোনো গণ-অভ্যুত্থান, বিপ্লব, গণ-আন্দোলন বা জনতার রায়কে ছোট বা অবেহেলার সুযোগ নেই। কোনো কিছুই নিরর্থক, অর্থহীন, কারণহীন ছিল না। প্রতিটি বিপ্লব ও আন্দোলনকে ধারণ করতে হবে এবং প্রতিটি থেকে শিক্ষা নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।
১৯৭১ সাল সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয় ঘটনা। এ দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইসিহাসে ৭১ সালের চেয়ে বড় কোনো ঘটনা নেই। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে ও অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে ৭১ সালে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। ৭১ এসেছিল আবার কয়েকটি ঢেউয়ের মাধ্যমে- যেমন- ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, ৬-দফা ও গণ-অভ্যুত্থান।
প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রয়েছেও এদেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ৪৭ সালেও এ দেশের মানুষ অনেক আশায় বুক বেঁধে ছিল ও পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে ছিল জমিদারি প্রথা ওঠে যাবে, জমির ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, অতিরিক্ত খাজনার হাত থেকে রেয়াই পাবে, এ দেশের মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারবে, চাকরি পাবে ইত্যাদি।
ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শাসনে মুসলমান ও তফসিলভুক্ত বা নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্র্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা একেবারে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিল। বাংলায় যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কথা আমরা বলে থাকি সেটা কেবল উচ্চ হিন্দু সমাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংখ্যায় মুসলমানরা ছিল বাংলার সংখ্যাগুরু কিন্তু তারপরেও পশ্চিমবাংলা তো বটেই খোদ পূর্ব বাংলাতেও স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতে মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ কর্মকর্তা/শিক্ষার্থী মুসলিম ছিল।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষাটা বুঝতে পেরে ১৯২৪ সালে বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানদের নিয়ে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন যা ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ খ্যাত নামে খ্যাত। তিনি বাঙালি মুসলমানদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন এবং যাতে বাঙালির ঐক্য তৈরি হয়। এই বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে সমতা আনার একটা প্রয়াস ছিল। তবে ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মারা গেলে এই বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ফলে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন যোগদান করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
বাঙালির পরাধীনতা বা অন্যের দ্বারা শোষিত হওয়ার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। যে কারণে চাকরিসহ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা খুব কমই কপালে জুটেছে। আশা করা হয়েছিল, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর কোনো বৈষম্য থাকবে না, সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিন্তু কিছু লোক তাদের সুবিধাবাদী চরিত্র বদলানোর পরিবর্তে আরও চরম আকারে চর্চা শুরু করে।
৭১ সালের পর এদেশে অনেক গণ-আন্দোলন হয়েছে। বন্দুকের নলের সামনে আগে আবু সাঈদের মতো কাউকে কখনও এমন বুকটান করে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।
শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। ‘ভাই পানি লাগবে কারও, পানি’ মুগ্ধের এ কথাটি এ দেশের মানুষকে সারা জীবন কাঁদাবে। খাবার পানি আর বিস্কুট বিতরণের সময় একটি গুলি তার কপাল ভেদ করে কানের পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়, লুটিয়ে পড়েন রাস্তায়।
জাতিসংঘের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় ১ হাজার ৪০০ লোক নিহত হয়েছেন। নিহতদের বেশির ভাগ ছাত্র, চাকরিপ্রত্যাশী, তরুণ ও শিশু-কিশোর। প্রতিটি মৃত্যই যেন এক একটা শোকগাথা। সাভারের আশুলিয়াসহ বিভিন্ন জায়গার হত্যাকাণ্ডের ভিডিও প্রকাশ হয়েছে যেগুলো দেখে মানুষ বাকরুদ্ধ, অসুস্থ হয়েছে।
আবু সাঈদ রংপুরের নীলগঞ্জ উপজেলার এক অজপারা গাঁয়ের ছেলে। অর্থাভাবে দিনমজুরের ছেলের লেখাপড়া হওয়া দুঃসাধ্যই ছিল। টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ চালাতেন। আবু সাঈদ সারা বাংলাদেশের প্রতীক, গুটি কয়েক পরিবার ছাড়া প্রায় সবার অবস্থা আবু সাঈদের মতো। এ দেশের লাখো শিক্ষার্থী কোনো না কোনো কষ্ট স্বীকার করে পড়াশোনা চালিয়ে যায়, একটি চাকরির আশায়, স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনের আশায়। স্বাধীনতার এত বছর পর স্বচ্ছ ও প্রশ্নহীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারাটাই জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য ‘লাইনঘাট, ‘সিস্টেম’ আর ‘মামু খালুর’ সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হয়। শুধু নিয়োগ প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের সব প্রতিষ্ঠান যেন ধ্বংস হতে বসেছিল। কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর এ দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না। পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন কমিশন সবখানে একই অবস্থা।
আমাদের দেশের মানুষ ভোটকে ‘উৎসব’ বলে মনে করে। ভোটের সময় দেশের গ্রাম-গঞ্জে গেলে বোঝা যায় এ দেশের মানুষ এই উৎসবে কতটা আগ্রহ নিয়ে শামিল হন। ভোট আসলে মেতে ওঠে তারা। সারা দিন ভোটের আলাপ-আলোচনা। চায়ের দোকান, হাটবাজার, মাঠ-ঘাট, অলিগলি, পাড়ামহল্লা সরগরম!
কিন্তু ইতিহাসের নিরিখে এ দেশের মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের খুব কমই মূল্যায়ন করা হয়েছে। অধিকার তো দূরের কথা, শত্রুতে পরিণত হওয়া নানা ধরনের ঝালেমায় পড়তে হয়েছে ভোটারদের। শুধু ক্ষমতা বদলের উপায় হয়ে আসে না, এ দেশের মানুষের জীবনে ভোট আসে বিভিন্ন রূপে। ভোটার থাকতে বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়া, পাতানো নির্বাচন, রাতের ভোট, ভোট ডাকাতি, ভোট জালিয়াতি, ভোট ম্যাকানিজম, বন্দুকের নল, বিভিন্ন বাহিনীর অত্যাচার, ভয়ভীতি দেখিয়ে সিল মারা, ভুতুড়ে ভোট, গায়েবি ভোট, টাকা পয়সার ছড়াছড়ি, বিরোধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়াসহ অনেক ঘটনা বারবারই এ দেশের গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এক ঝামেলা চলে গেলে আর এক ঝামেলা এসে জেঁকে বসেছে।
এটাই এ দেশের বাস্তবতা যে, ক্ষমতাসীন বা দলীয় সরকারের অধীনে কোনো জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ), দ্বিতীয়, তৃতীয় (১৯৮৬) ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৮৮) নিয়ে বিতর্ক ছিল।
একসময় সব দল এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পতন ঘটায় যেটা ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এরশাদের পতনের পর একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় যার অধীনে ১৯৯১ সালের নির্বাচন হয়। ওই অন্তর্বর্তী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ বলা না হলেও মডেলটা ছিল সেরকমই।
ব্যাপক আন্দোলন সংগ্রামের পর বিএনপি ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আইন পাস করে। তবে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন অতীত অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে ২০০১ ও ২০০৮ সালে এই সরকারের গঠন নিয়ে অসন্তোষ দেখা যায়। তবে ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন মোটামুটি নিরপেক্ষ হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল- এ বিষয়ে কারোর দ্বিমত থাকার কথা নয়।
২০০৮ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা ত্রুটি দেখিয়ে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের উদ্যোগ নেন। ফলে যে তরি চড়ে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছিল, সেটা আর থাকল না।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া পরপর তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল বিরোধীদের নির্বাচনে আনতে না পারা।
সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চা, জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকার ও সংসদে সত্যিকার অর্থে বিরোধী দল খুবই আবশ্যক। আর স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান না গড়ে, সুস্থ গণতন্ত্র চর্চা না করে, দেশে অসন্তোষ থাকলে কিছু যে টেকসই হয় না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
বিগত দিনে লক্ষণীয়, কিছু মানুষের মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা কাজ করছে, কীভাবে দ্রুত সময়ে অঢেল ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সার মালিক হওয়া যায়। ব্লুমবার্গ, পানামা পেপারস ও প্যান্ডোরা পেপারস, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতো বিভিন্ন সংস্থা ও দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম কিছুদিন পর পর কিছু মানুষের অবৈধ ধন-সম্পদ ও অর্থ পাচারের রিপোর্ট বা খবর প্রকাশ করেছে।
পৃথিবীর অনেক দেশে দুর্নীতি, লুটপাট ও অপকর্ম রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ অপকর্ম-দুর্নীতি একটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়। যার বর্ণনা দিতে একেকজনের জন্য বই ছাপানোর প্রয়োজন পড়ে। হাজার বিঘার ওপরে ভূমি, দেশে-বিদেশে অসংখ্য ফ্ল্যাট, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট, দেশে-বিদেশের ব্যাংক ও কোম্পানিতে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রভৃতি। অনেকে টাকা পাচারের জন্য নিজেরাই চালু করে মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান।
রাষ্ট্রীয় দমন, বৈষম্য, কোটানীতি, দুর্নীতি, বিচারহীনতা ও শাসনব্যবস্থার অব্যবস্থা, অন্যায়, দমন-পীড়ন বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত হয়। বিপ্লব সবসময় এক ধাক্কায় আসে না, বরং ধাপে ধাপে, ঢেউের পর ঢেউ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, ধীরে ধীরে লক্ষ্যে পৌঁছায়। যেমনটা ফ্রান্সে এসেছিল।
একটা বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর একটা দেশ বা সমাজ একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও যায়। বার বার বিপ্লব, বার বার রক্ত দেয়া কাম্য নয়। সব দেশ বা সমাজ এর ধকল নিতে পারে না। বারবার এমনটা ঘটতে থাকলে দেশ একটি সংঘাতময় ও অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকেই চলে যায়।
নতুন কোনো বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার আগেই রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারণী মহল বিশেষ করে যারা শাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িতদের জনগণের মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে পারা ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়াটা সবার জন্য মঙ্গলকর।
লেখক: গণমাধ্যম কর্মী
 প্রিন্ট করুন
প্রিন্ট করুন

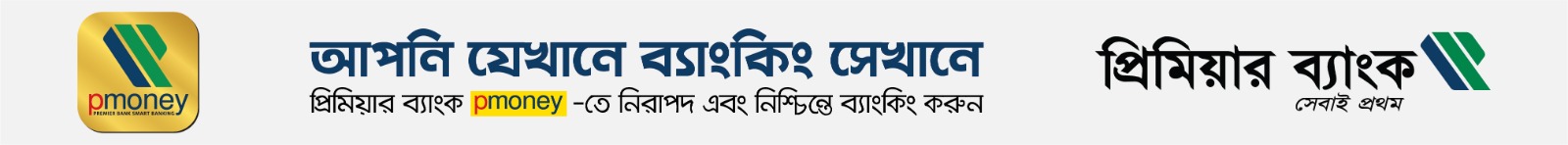












Discussion about this post